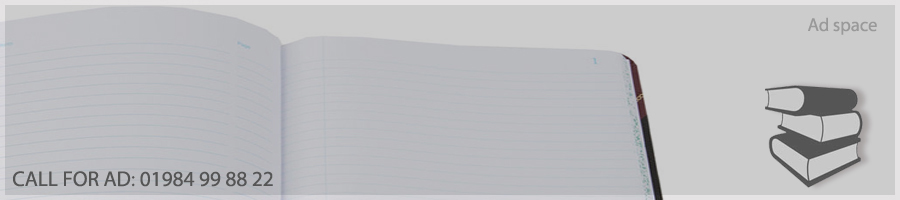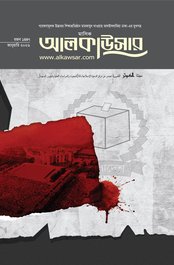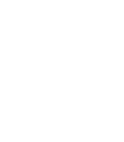জুলাই ঘোষণাপত্র
‖ একপেশে দায়সারা ভুল ইতিহাস চর্চা—এটির দরকার ছিল কি?
অবশেষে গত ৫ আগস্ট ২০২৫ ঈ. জুলাই ঘোষণাপত্র এসেছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সাথে নিয়ে ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেন। সরকারিভাবে এটিকে বেশ গুরুত্ব সহকারে প্রচার করা হয়। যদিও ওই ঘোষণাপত্রে সাধারণ জনগণের তেমন কোনো আগ্রহ ছিল বলে মনে হয়নি। ঘোষণাপত্র প্রকাশের পর তো এমন কোনো দল বা গোষ্ঠী পাওয়া যায়নি, যারা এতে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হয়েছে।
কেন এমন হল?
২০২৪ সালের আগস্টের শুরুতে ইতিহাসের জঘন্যতম ফ্যাসিবাদ থেকে বাংলার মানুষ মুক্তি পেয়েছিল ছাত্রজনতার এক রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। তারই ধারাবাহিকতায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। তখন থেকেই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীগণ এবং দেশের সচেতন সাধারণ জনগণের পক্ষ থেকে একটি ঘোষণাপত্র ও জাতীয় সনদ তৈরির দাবি ওঠে। দেরিতে হলেও কয়েক মাস আগে আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ছাত্রদের পক্ষ থেকে জুলাই ঘোষণাপত্র প্রকাশ করার ঘোষণা আসে। কিন্তু ড. ইউনূস সরকার তাতে বাঁধ সাধে। তারা নিজেরাই এ ঘোষণাপত্র পেশ করবেন বলেন।
তারপর পেরিয়ে যায় অনেক দিন। ততদিনে সরকারের অবস্থান বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। জনগণের কাছে মনে হতে থাকে, সরকারের হাত-পা কোথায় যেন বাঁধা আছে। এমনই এক সময়ে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ৫ আগস্টের অভ্যুত্থান বার্ষিকীতে জুলাই ঘোষণাপত্র আনবে।
২০২৪ সনের অভ্যুত্থানের পর দেশের মানুষ আশায় বুক বেঁধেছিল। তারা আশা করেছিল, ছাত্রজনতার পক্ষ থেকে যে সরকারকে অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তারা মৌলিকভাবে ভেঙে পড়া আইনশৃঙ্খলার উন্নতি সাধন, বিগত ফ্যাসিবাদী সরকারের পক্ষ থেকে যেভাবে রাষ্ট্রীয় কাঠামোগুলোর সর্বস্তরে ধ্বংস টেনে আনা হয়েছিল, সেগুলোর মেরামত এবং ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের আর কোনো ফ্যাসিবাদ দেশের জনগণের ওপর মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে, তা নিশ্চিত করবে। কিন্তু সরকারের বিদায় ঘণ্টা বেজে গেলেও (ড. ইউনূসের ঘোষণা অনুযায়ী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তাদের বিদায় ঘটবে) এসকল ক্ষেত্রে বলতে গেলে কিছুই করতে পারেনি তারা। তাই এ সরকারের কাছে জুলাই ঘোষণাপত্র শোনার আগ্রহ বা ইচ্ছা জনগণের ছিল বলে মনে হয়নি।
তাঁরা যদি এ ধরনের ঘোষণাপত্রকে গুরুত্বের সাথে নিতেন, তাহলে ক্ষমতায় বসার দুয়েক মাসের মধ্যেই প্রকাশ করতে পারতেন। তখন তাদেরকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাছে ধরনা দিতে হত না। তাদের ইচ্ছা পূরণের চাপ নিতে হত না। বদনামও সইতে হত না। একটি দলের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগও শুনতে হত না। সাথে সাথে এই ঘোষণাপত্রের ফুল স্পিরিটও বজায় থাকত। কিন্তু সরকারের সময়োচিত সিদ্ধান্তের অভাব অথবা তাদের অনাগ্রহ এ ঘোষণাপত্রটিকে আকর্ষণহীন করে তুলেছে।
কী আছে ঘোষণাপত্রে?
তেমন আগ্রহ না থাকলেও দুকলম লেখার প্রয়োজনে ঘোষণাপত্রটি আদ্যোপান্ত একাধিকবার পড়া হয়েছে। মতলববাজ ও মিথ্যাবাদীরা ছাড়া ঘোষণাপত্রের এক নম্বর ধারা পড়লে যে কেউ বুঝতে পারবে, এটি স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে আরম্ভ করে এত বছর যাবৎ দেশকে ও দেশের জনগণকে শোষণ করা এবং বিভিন্নভাবে জনগণের অর্থ সম্পদ ও রাষ্ট্রীয় সুবিধা বাগিয়ে নেওয়া মতলববাজ রাজনীতিবিদ, একশ্রেণির লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের ভাষা অনুসরণ করা হয়েছে তাতে।
ঘোষণাপত্রের ১নং ধারার শুরুতে লেখা হয়েছে– ‘যেহেতু উপনিবেশবিরোধী লড়াইয়ের সুদীর্ঘকালের ধারাবাহিকতায় এই ভূখণ্ডের মানুষ দীর্ঘ ২৩ বছর পাকিস্তানের স্বৈরশাসকদের বঞ্চনা ও শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল এবং নির্বিচার গণহত্যার বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করে জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল।’
কোনো জ্ঞানী বা সৎ লোক কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন– এটি সত্য কথা? উপনিবেশ বলতে কী বোঝানো হচ্ছে? নিশ্চয়ই ইংরেজদের এ অঞ্চলে আগ্রাসন এবং ২০০ বছরের মতো ভারতীয় উপমহাদেশকে শাসন করার কথা। তো ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ (অখণ্ড পাকিস্তান আমল) উপনিবেশবাদ হয়ে গেল কীভাবে? ওই সময়টাকে উপনিবেশবাদের ধারাবাহিকতা কীভাবে বলা হচ্ছে? ১৯৪৭ সনের ১৪ আগস্ট যে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি গঠিত হয়েছে, তা কি শুধু পশ্চিম পাকিস্তানীদের চেষ্টা ও অবদানে গঠিত হয়েছে, নাকি ইংরেজদের থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্র আদায় করে নেওয়ার পেছনে আমাদের এ অঞ্চলের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সাধারণ জনগণের সমান অংশগ্রহণ ছিল। বরং যে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পরবর্তীতে পাকিস্তান রাষ্ট্র হয়েছে, সেটিও তো এ অঞ্চলের একজন নেতাই পাঠ করেছিলেন। বাঙালি নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আব্দুল হামীদ খান ভাসানী, এ কে ফজলুল হকসহ কোন্ বড় নেতা ছিলেন না পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে? এমনকি শেখ মুজিবুর রহমান, যিনি তখন ছাত্র ছিলেন, তিনিও মুসলিম লীগের ছাত্র ফোরাম থেকে পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করেছেন। তাহলে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন এবং তার পরবর্তীতে ৪৭ থেকে ৭১-এর সময়কে উপনিবেশবাদের ধারাবাহিকতা বলা হচ্ছে কোন্ যুক্তিতে? কাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে?
এ কথা ঠিক, পাকিস্তান যে উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল এবং মুসলমানরা যে ভ্রাতৃত্ব, সাম্য, ন্যায়বিচার ও ইসলামের শাশ্বত ব্যবস্থা কায়েমের আশায় বুক বেঁধেছিল, তার কোনোটাই দেশটির বিভিন্ন সময়ের শাসকরা পূরণ করতে পারেনি। দেশের সর্ববৃহৎ প্রদেশ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান তার ন্যায্য হিস্যা পায়নি। একাধিকবার দীর্ঘ সামরিক শাসনের মাধ্যমে একনায়কতন্ত্র কায়েম করে রাখা হয়েছিল।
সর্বশেষ ১৯৭০-এর নির্বাচনে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যাদেরকে ভোট দিয়েছে, তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়নি। যার দরুন এ অঞ্চলে প্রথমে ব্যাপক গণ আন্দোলন এবং পরে স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা হয়। সর্বশেষ ১৯৭১ সনের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানী সেনাদের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ নামে নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।
১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র জন্ম নেওয়ার পর থেকে ২৫ বছরের মতো অখণ্ড ছিল। আমাদের এ অঞ্চল তখন ‘পূর্ব পাকিস্তান’ হিসেবে অবহিত হত। যা ছিল পাকিস্তানের বৃহত্তর প্রদেশ। এ দীর্ঘ প্রায় সিকি শতাব্দীর মধ্যে বাংলা অঞ্চলের কোনো নেতা কি কখনো ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, পাকিস্তান গঠন করা ভুল হয়েছিল? দ্বিজাতিতত্ত্ব ঠিক ছিল না? এমনকি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হয়ে ওঠা শেখ মুজিবও কি কখনো বলেছিলেন যে, পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন ঠিক ছিল না?
তাহলে কেন এ মিথ্যাচার করা হচ্ছে? ইতিহাস তো ভিন্ন কথা বলে। শুধু শেখ মুজিব কেন, তার সাথে এ অঞ্চলের অন্যান্য নেতারাও তো স্বতঃস্ফূর্তভাবেই পাকিস্তানের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন। এবং ২৫ শে মার্চ পাকিস্তান আর্মির হাতে বন্দি হয়ে করাচি চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি অখণ্ড পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার চেষ্টা করে গেছেন। তাহলে কেন এ অসত্য উচ্চারণ?
কেউ কেউ বলে থাকেন, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষ দ্বিজাতিতত্ত্ব ত্যাগ করেছে। সত্যিই কি তাই? যদি এমনটি হত, তাহলে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র হত না; বরং সকলে তওবা করে এ অঞ্চলকে ভারতের সাথে একাকার করে ফেলত।
এ কথা কে না জানে, পূর্ব পাকিস্তানের নেতাদের সাথে এ অঞ্চলের রাজনীতিকদের মূল সমস্যাটাই ছিল ক্ষমতাকেন্দ্রিক এবং বৃহত্তর প্রদেশ হিসেবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এ অঞ্চলের উন্নয়নে ভূমিকা না রাখার কারণে। এর সাথে দ্বিজাতিতত্ত্বের আদৌ কোনো সম্পর্ক ছিল না। এ অঞ্চলের ধর্মবিদ্বেষী যেসকল ভুঁইফোঁড় রাজনীতিক, সাংবাদিক ও বিভিন্ন পেশাজীবী বাংলাদেশ হওয়ার কারণে পাকিস্তানকেই গলদ বলছে, যদি পাকিস্তান রাষ্ট্র এবং পরবর্তীতে তা থেকে বাংলাদেশ গঠিত না হত, তাহলে এদের কি কোনো পাত্তা থাকত? এদেরকে কেউ চিনত? তবুও স্বাধীন বাংলাদেশের (যা মূলত পাকিস্তান গঠিত হওয়ার ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে) ভাত ও আবহাওয়া ভোগ করেও তাদের দিল মন লেগে থাকে হিন্দুত্ববাদী ভারতের মধ্যে।
এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ মানুষের বিশ্বাস ও নীতি আদর্শের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে তারা বিদেশি প্রভুদের চিন্তা-চেতনাকেই এদেশের মানুষের চিন্তা বলে জোর করে চাপিয়ে দিতে চায়। ইসলাম ও ইসলামী আদর্শের নাম শুনে তাদের গাত্রদাহ হয়। সম্ভবত সেই সংখ্যালঘু মুষ্টিমেয় লোকের ফাঁদে পা দিয়েই জুলাই ঘোষণাপত্রের এক নম্বর ধারায় পাকিস্তান আমলকেও উপনিবেশবাদ বলে বিতর্কিত হয়েছে ড. ইউনূস সরকার।
কেন এ আপত্তি?
অনেকেই মনে করতে পারেন, জুলাই ঘোষণাপত্রের সব ধারা তো সামনে থেকেই গেছে। এতটুকু কথা নিয়ে এত আপত্তির কী আছে? কিন্তু একটু গভীরে ঢুকলেই বিষয়টি উপলব্ধি করা যাবে। এর জন্য একটু পেছনে যাওয়া যেতে পারে। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর যখন স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হল, তখন দেশের শাসনভার আওয়ামী লীগ হাতে নিয়ে একটি সংবিধান প্রণয়ন করল। ডক্টর কামাল হোসেনরা বেশিরভাগ সময় ভারতে বসে সংবিধান নামক একটি জিনিস তৈরি করে আনলেন। সে সংবিধানের প্রস্তাবনাতেই এমন সব কথা জুড়ে দেওয়া হয়, যার সাথে দেশের সাধারণ বাঙালি জাতি ও সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধাদের (দুয়েকজন ব্যতিক্রম থাকতে পারেন) কোনো সম্পর্ক ছিল না।
সংবিধানের প্রস্তাবনায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার মূল উদ্দেশ্য হিসেবে যে চারটি বিষয় আনা হয়েছে, তার মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রকেও সন্নিবেশিত করা হল। অথচ পুরো স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বা এর পূর্ববর্তীতে ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ছয় দফা, সত্তরের নির্বাচনসহ কোনো সময়ই আওয়ামী লীগসহ বড় কোনো রাজনৈতিক দল ধর্মনিরপেক্ষতার দাবি তোলেনি।
সমাজতন্ত্র কখনো এ অঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে আদর্শ ছিল না, এখনো নেই। খোদ সমাজতন্ত্রীরাই বুর্জোয়া রাজনীতিকদের (তাদের ভাষা অনুযায়ী) কোলে আশ্রয় নিয়েছে অনেক আগেই। তবুও ইসলামবিদ্বেষী শক্তি পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়ে যাওয়াকে তাদের মতলবে ব্যবহারের প্রয়াস পেয়েছে। পাকিস্তানের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ গঠিত হলেও এদেশের সংবিধানে ইসলাম ও মুসলমানদের চিহ্ন পর্যন্ত রাখা হয়নি।
এরপর আওয়ামী লীগের প্রথম একনায়কবাদী সরকারের বিদায়ের পর যখন জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি হন, তখন তিনি কিছুটা হলেও এ মিথ্যার কলঙ্ক থেকে জাতিকে মুক্ত করতে চেষ্টা করেন। তিনি সংবিধানের প্রস্তাবনায় ধর্মনিরপেক্ষতার স্থলে আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস এবং ‘সমাজতন্ত্র’-এর জায়গায় ‘সামাজিক সাম্য ও ন্যায় বিচার’ অন্তর্ভুক্ত করেন। যোগ করেন ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’। জিয়ার এ কাজের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় ভিন্ন কারণে। তিনি শুধু মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডারই ছিলেন না; বরং ছিলেন স্বাধীনতার ঘোষকও। যদিও ৭২-এর সংবিধানের মূল কাঠামো অক্ষুণ্নই থেকে গিয়েছিল, তবুও মরহুম জিয়াউর রহমান কর্তৃক এতটুকু সংশোধনী আনাতে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ মানুষ কিছুটা হলেও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল এবং সেটির সুফলও জিয়া প্রতিষ্ঠিত দল বিএনপি ভোটের মাধ্যমে বারবার পেয়েছে। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারী ও মতলবিরা থেমে থাকেনি। আওয়ামী ফ্যাসিবাদ ও তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দোসররা কখনো ইসলাম ও সত্যিকারের ইসলামপন্থিদের সহ্য করতে পারেনি। গত দশকে বিচার বিভাগের কলঙ্ক হিসেবে খ্যাতি পাওয়া খাইরুল হকের রায় দিয়ে শুরু করে পরবর্তীতে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে আবার মিথ্যার যুগে ফেরত নিয়ে যাওয়া হয় সংবিধানের প্রস্তাবনাকে। খাইরুল হক যখন পঞ্চম সংশোধনীর ওই অংশগুলো বাদ দিয়ে রায় প্রদান করেন, তখনই আমরা কাজটিকে মতলবি ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে আখ্যায়িত করেছিলাম, যা সে সময় আলকাউসারসহ দেশের বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছিল। আজকে যখন জুলাই ঘোষণাপত্রে প্রথম লাইনেই আমরা সে কুমতলবিদের ভাষা দেখতে পাই, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না, এ দেশের কোটি মানুষের আকাক্সক্ষার বিপরীতে গিয়ে ইউনূস সরকার কাদের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন!
জুলাই ঘোষণাপত্রে ‘যেহেতু যেহেতু’ বলে ২০টি ধারা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোতে মূলত জুলাই অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট সংক্রান্ত বিষয় আনার চেষ্টা করা হয়েছে। এরপর ‘সেহেতু সেহেতু’ বলে আনা হয়েছে আরও পাঁচটি ধারা। যেগুলোতে ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং অঙ্গীকার করা হয়েছে।
একটু গভীরভাবে দেখলেই বোঝা যাবে, এ ঘোষণাপত্র শুধু একপেশে ও অসম্পূর্ণই নয়; বরং অনেকটা কথার কথা ও দায়সারা গোছেরও বটে। ভাবটা এমন যে, একটি ঘোষণাপত্র দিতে হবে, তাই দিয়ে দিলাম। যদি গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আনা হয় এবং হাসিনার আওয়ামী ফ্যাসিবাদের পতনের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগের ইতিহাস দেখা হয়, তাহলে তো শুরুতেই এদেশের ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর অসাধারণ ত্যাগ এবং তাদের ওপর হাসিনার অত্যাচারের খড়্গের কথা আনা দরকার ছিল। যার সবচেয়ে বড় উদাহরণ ‘শাপলা ট্র্যাজেডি’। ২০১৩ সালের মে মাসে শাপলা চত্বরে হাসিনাবিরোধী জনস্রোতের ওপরে যে গণহত্যা আওয়ামী সরকার চালিয়েছিল, তা তো এদেশের ইতিহাসে এখনো পর্যন্ত নজিরবিহীন হয়ে রয়েছে।
এককভাবে বিবেচনায় নেওয়া হলে বাংলাদেশে স্বৈরাচারী হাসিনাকে কার্যকরভাবে ইসলামপন্থিরাই বারবার চ্যালেঞ্জ করেছে। এমনকি ২০০১ সালে যে বিএনপি দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি আসনে বিজয়ী হয়েছে, তার পেছনেও ছিল ৯৬ পরবর্তী হাসিনা সরকার কর্তৃক ইসলামপন্থিদের ওপর দমন-পীড়ন এবং তার প্রতিক্রিয়ায় দেশব্যাপী হাসিনাবিরোধী গণ আন্দোলনের ফসল। তো এই যে ফ্যাসিবাদের পতনের কথা বলতে গিয়ে শুধু ২০২৪ সালের কথাই এল, তা কি বাস্তবসম্মত ও যুক্তিসম্মত হয়েছে!? অন্তত শাপলা হত্যাকাণ্ড এবং ঐ সময়ের আন্দোলনের স্বীকৃতি তো এ ঘোষণায় রাখা অনিবার্য ছিল। ব্যাপারটি ওদের মতো হয়ে গেল, যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস ১৯৭১ থেকে শুরু করে সেখানেই শেষ করে। অথচ এ জাতি স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে বারবার এবং বিজয়ও পেয়েছে একের পর এক। যার সর্বশেষটি ১৯৭১ সালে সূচিত হয়েছে।
স্বাধীনতার ইতিহাস ৭১ সাল থেকে শুরু করলে তা যেমন বংশ বর্ণনা ছাড়াই নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় দেখানো হয়, হাসিনার পতনের ক্ষেত্রে পেছনের সময়ের বড় বড় অবদানগুলোর স্বীকৃতি না দেওয়াও সংকীর্ণতা ও পক্ষপাতিত্বের মধ্যে পড়ে। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই এদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ তাদের নারাজির কথা প্রকাশ করেছেন।
ঘোষণাপত্রটি পড়লে স্পষ্টতই দেখা যায়, এতে পতিত আওয়ামী লীগের কিছু মোটা দাগের দোষত্রুটির কথা বলা হয়েছে এবং পরোক্ষভাবে আরেকটি দলকে আনুকূল্য দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।
সরকার হয়তো ঐ দলটির পক্ষ থেকে চাপে ছিল। তারা হয়তো ভেবেছে, এ দলটিকে অখুশি করলে তারা ঘোষণাপত্র মেনে নেবে না। এই যে বর্তমান সরকারের এহেন একপেশে মনোভাব, তা কিন্তু শুধু ঘোষণাপত্রের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রেও বিশেষত সংস্কার বিষয়ক ঐকমত্য কমিশনের ওপর তো অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতাদের বরাবরই অনুযোগ লেগে আছে যে, অন্য সকলে মিলে কোনো বিষয়ে একমত হলেও শুধু একটি দলের বিরোধিতার কারণে অনেক সিদ্ধান্তই বানচাল হয়ে যাচ্ছে। এখানে একটি দলের পক্ষ-বিপক্ষ নেওয়ার বিষয়ে কথা বলতে চাই না, দেশের একজন নাগরিক হিসেবে আমাদের প্রশ্নটা অন্য জায়গায়।
রাজনৈতিক দলগুলো কি দেশের মালিক?
দেশের সচেতন নাগরিকদের সাথে আমাদেরও প্রশ্ন এই যে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সংবিধান সংশোধনসহ বিভিন্ন সংস্কার বিষয়ে রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ ও সর্বস্তরের মানুষের রায় নিয়েছে, সেটি তো একটি ভালো পদক্ষেপ ছিল। কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে এখন তো তারা শুধু রাজনৈতিক দলগুলোর সাথেই বোঝাপড়া করছে। ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছে যে, রাজনৈতিক দলগুলো যা বলবে, সেটাই জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। তাও আবার প্রভাবশালী বড় দল হলে তারটাকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে। তা না হলে সংস্কার বিষয়ে এবং সংবিধান সংশোধন বিষয়ে দেশের সাধারণ মানুষ যেসকল প্রস্তাব দিয়েছে, সেগুলো কেন ঐকমত্য কমিশন আমলে নিচ্ছে না। এমনকি তাদের নিজেদের জরিপের মাধ্যমে জনগণের যেসকল বক্তব্য পাওয়া গেছে, সেসব বিষয়ে তো তারা নিশ্চুপ। এদেশের জনগণ ইসলাম চায়। ইসলামী সরকার চায়, কেবল কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন না করার প্রতিশ্রুতি চায় না।
ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতামত পাওয়া এসকল জরিপের কোনো তোয়াক্কা কি অন্তর্বর্তী সরকার করছে? এমনিতে তো বলা হয়ে থাকে, সংবিধানে বলা আছে, দেশের নাগরিকগণ রাষ্ট্রের মালিক (যদিও নাগরিক এবং রাষ্ট্র সব কিছুরই প্রকৃত মালিক সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা); কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তো রাজনীতিকদেরকে রাষ্ট্রের মালিক মনে করা হচ্ছে। যেসকল লোক ঐকমত্য কমিশনে বসে বিভিন্ন পয়েন্টে দর কষাকষি করছেন, দেশের কয় ভাগ লোকের সমর্থন তাদের প্রতি আছে। কিন্তু একতরফাভাবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর মতামতকেই চূড়ান্ত ধরে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এটিই যদি হবে, তাহলে এসব করে এতদিন ক্ষমতায় থাকার দরকার ছিল কি? ক্ষমতায় বসার পরপর নির্বাচন দিয়ে রাজনীতিকদের হাতে রাষ্ট্র ছেড়ে দিলেই তো হত। দেশের জনগণ তো তাদেরকে এ আশায় ক্ষমতায় থাকতে সম্মতি দিয়েছে, যেন তারা অতি দ্রুত প্রয়োজনীয় সংস্কার সেরে নিতে পারে। কিন্তু তারা সবকিছুই দলীয় রাজনীতিকদের খুশি রেখে করতে চান। এ যেন গরুকে জিজ্ঞেস করে হালচাষে নেওয়া।
যাহোক, বলা হচ্ছিল, জুলাই ঘোষণাপত্রটিতে একটি দলের প্রতি আনুকূল্য সুস্পষ্ট।
জুলাই ঘোষণাপত্রে বিগত ফ্যাসিবাদী সরকারের লোকদের বিচারের কাঠগড়ায় আনার যে প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে, এ মুহূর্তে এমন কথা অনেকটা লোকদেখানো এবং বলার জন্য বলা। জুলাই ঘোষণাপত্রটি যদি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় বসার দুয়েক মাসের মধ্যে এসে যেত, তাহলে অন্য কথা ছিল। কারণ সরকার ক্ষমতায় বসেছে এক বছর পার হয়ে গেছে। এ সময়টি অনেক দীর্ঘ না হলেও এধরনের সরকারের জন্য একেবারে কমও নয়। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এখন পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারো বিচার সম্পন্ন হয়নি। আর ফ্যাসিবাদের দোসরদের (আমলা, সামরিক-বেসামরিক কর্মচারী, সাংবাদিক, ভিসি ও শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, সুশীল সমাজ, ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন গোষ্ঠীর ওইসকল লোকজন, যারা জেনে-বুঝে পতিত আওয়ামী সরকার ও হাসিনার সকল কাজকে বৈধ ও ভালো বলে প্রচার করে গেছে) প্রায় সকলেই তো নির্বিঘ্নে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা নিয়ে জীবনযাপন করছে। তাদের বিচার করা তো দূরের কথা, তাদের নামে কোনো মামলাও দায়ের করা হয়নি। অনিবার্যভাবে যার খেসারত দেশ ও জনগণকে দিতে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও দিতে হবে। এখন তো দোসরদের অনেকেই পরিপূর্ণ ছাড় পেয়ে আবার পুরোনো চরিত্রে ফিরে যাচ্ছে। সাংবাদিক নামধারী যেসকল দালাল চক্র, মিডিয়া হাউসের মালিকেরা, সুশীল সমাজের লেবাসধারী চাটুকারেরা, শিক্ষাবিদের লেবাসধারী জ্ঞানপাপীরা এখন তো পুনরায় আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে আনার ও প্রতিষ্ঠিত করার প্রচারণায় লেগে গেছে। তাদের এই দুঃসাহসের দায় কি এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নয়। সরকার ক্ষমতায় বসেই যদি ওদের কঠিনভাবে পাকড়াও করত, তাহলে কি আজ তারা এ স্পর্ধা দেখাতে পারত!?
প্রসঙ্গ : বানোয়াট নির্বাচন
ঘোষণাপত্রের ১৩ নম্বর ধারায় ২০১৪, ২০১৮, ২০২৪-এর প্রহসনের নির্বাচনের প্রসঙ্গ এসেছে। কিন্তু যে দলই ক্ষমতায় যাক, এই নির্বাচনগুলো বাতিল ঘোষণা করা হবে এবং এর সাথে জড়িত ব্যক্তিদের কঠিন শাস্তির আওতায় আনা হবে– এমন কোনো বক্তব্য ঘোষণাপত্রে নেই। যদি ব্যাপারটি এমনই থাকে যে, নির্বাচনের শুধু বদনাম হল, কিন্তু সব আইনগতভাবে বৈধ থেকে গেল, তাহলে ভবিষ্যতেও কোনো স্বৈরাচার পুনরায় এ ধরনের পাতানো নির্বাচনের খেল দেখাতে পারে।
পেছনে ফিরলে দেখা যাবে, স্বৈরাচারী সামরিক শাসক এরশাদ তার শাসনামলে দুটি পাতানো নির্বাচন করেছে। ১৯৮৬ ও ১৯৮৮-এর সে নির্বাচনগুলো ছিল ভোটারবিহীন ও সাজানো। স্বৈরাচারী এরশাদ পতনের পর বিএনপি ক্ষমতায় বসেছে। তারা চেষ্টাও করেনি ওই নির্বাচনগুলো বাতিল করার এবং এর সাথে জড়িত নির্বাচন কমিশনসহ মূল সহযোগীদের বিচারের আওতায় আনার! এমনটি করা হলে পরবর্তী যুগে এসে আওয়ামী লীগ হয়তো পাতানো নির্বাচনের এমন খেলা দেখানোর সাহস করত না।
কেউ হয়তো ভাবতে পারেন, নির্বাচন বাতিল করলে ওই সরকার যেসকল কাজ করে গেছে, সেগুলোর কী হবে?
এর জবাব তো সহজ, বিভিন্ন সময় আদালত কোনো ব্যক্তির নিয়োগকে অবৈধ বলে থাকে, কিন্তু এতদিন সে যে কাজ করেছে, সেগুলোর মধ্যে নিয়মসম্মত কাজগুলোকে বৈধতা দিয়ে দেয়। তো নির্বাচন অবৈধ ঘোষণা করতে হলে ওই সরকারগুলোর নিয়মসম্মত কাজকে বৈধতা দিয়েও তো তা করা যায়। কিন্তু এদেশে ‘যে লাউ সেই কদু’র ধারা চলছেই।
মনে হচ্ছে, গতানুগতিক রাজনৈতিক দলগুলোর মতো অন্তর্বর্তীকালীন সরকারও জনগণের চোখে ধুলো দিয়ে সময় পার করতে চায়। কোথায় গেল ড. ইউনূসের সেসকল কথা, ‘রাষ্ট্র মেরামতের এ সুযোগ হাতছাড়া করবেন না’, ‘এ সুযোগ আর আসবে না’! কোথায় গেল ফ্যাসিবাদীদের বিচার করার দৃঢ় প্রত্যয়? এখন তিনি নিজেই তো বিদায়ের দিনক্ষণ জানিয়ে দিয়েছেন। তার হাতে বলতে গেলে তো আর কয়েক মাস আছে। তফসিল ঘোষণা হয়ে গেলে নিয়ম অনুযায়ী অনেক দফতরই নির্বাচন কমিশনের এখতিয়ারে চলে যাবে।
প্রসঙ্গ : জাতীয় পার্টি
ঘোষণাপত্রে ক্লিনচিট পেয়ে গেছে প্রয়াত জেনারেল এরশাদের জাতীয় পার্টি ও তার নেতারা। এদের বিষয়ে কোনো অঙ্গীকারই করা হয়নি। অথচ ফ্যাসিবাদের উচ্ছিষ্টভোগী এ গৃহপালিত বিরোধী দলটি পতিত আওয়ামী সরকারকে কাগজে-কলমে বৈধতা দেওয়ার কাজ করে গেছে এই দীর্ঘ সময়। এরশাদ তো মৃত্যু পর্যন্ত শুধু তথাকথিত বিরোধী দলীয় প্রধানই থাকেননি; বরং মন্ত্রী পদমর্যাদায় হাসিনার উপদেষ্টা পদে থেকে জনগণের কষ্টার্জিত করের অর্থ কাজ না করেই ভোগ করে গেছেন। সাথে বোনাস হিসেবে পেয়েছেন হাসিনার অনুগত আদালতগুলোতে অনেকটা নিশ্চিত মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার মতো মামলার চূড়ান্ত রায় থেকে অব্যাহতি। এত বছর হাসিনার উচ্ছিষ্ট ভোগ করা এরশাদ-দলীয় সেসকল নেতারা এখন তো প্রকাশ্যেই দল গোছানোর চেষ্টা করছে। এর মানে তারা সামনেও নির্বাচন করতে পারবে। জনগণের কাছে তো এটা অনভিপ্রেত; আওয়ামী লীগ আগামী নির্বাচনের বাইরে থাকবে, কিন্তু তার দোসর জাতীয় পার্টি নির্বাচনে অংশ নেবে! অথচ এরা তো একে অন্যের মাসতুতো ভাই। যাদেরকে অবশ্যই বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো উচিত।
ঘোষণাপত্রে সাংবিধানিক সংস্কার
জুলাই ঘোষণাপত্রে সাংবিধানিক সংস্কারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সে সংস্কার কী– সেটা খোদ ঘোষণাকারীদেরই অজানা। কারণ তারা এতদিনেও কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। এখন তো মনে হয়, এসব খেলা বন্ধ হওয়া দরকার। এ সরকারের দক্ষতা জনগণ তো দেখে নিয়েছে। তাদের দৌড় কতটুকু তা ইতিমধ্যেই বোঝা গেছে। সুতরাং ঘোষিত সময়ে নির্বাচন হলে সংবিধান সংস্কারের বিষয়ে পরবর্তী সংসদই সিদ্ধান্ত নেবে।
আমরা খুব বিনয়ের সাথেই বলতে চাই, দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এই ঘোষণাপত্রটি আসলে পর্যালোচনা-যোগ্যই হয়নি বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞজনেরা। তবুও আলকাউসারের পাঠক মহলের অনুরোধে দু-চারটি কথা আরজ করা হল।