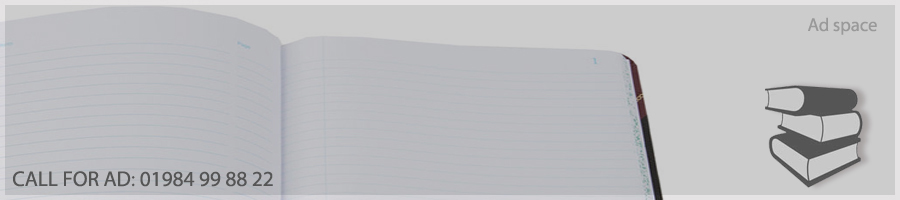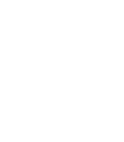বর্তমান বিশ্বে হাফেয গড়ার অন্যতম কারিগর গওহরডাঙ্গার হাফেয আবদুল হক রহ.
হাফেয মোহাম্মদ খালেদ
হাফেয মোহাম্মদ খালেদ বিংশ শতকের প্রখ্যাত হাফেযে কুরআন, বাংলার ঘরে ঘরে হেরার জ্যোতি বিতরণের স্বার্থক অভিযাত্রী, বর্তমান বিশ্বে হাফেয গড়ার অন্যতম কারিগর আলহাজ্ব হাফেয আবদুল হক ছাহেব গত ২৯ জানুয়ারি ২০০৯ ইং রোজ বৃহস্পতিবার রাত ৮টায় ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিঊন। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. প্রতিষ্ঠিত বাংলার প্রাচীনতম দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গোপালগঞ্জ জেলার অর্ন্তগত দারুল উলূম খাদেমুল ইসলাম গওহরডাঙ্গা মাদরাসার হেফয বিভাগের প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। আল কুরআনের প্রচার-প্রসারে নিবেদিতপ্রাণ এ মহাপুরুষ হাফেয গড়ার ক্ষেত্রে কি পরিমাণ অবদান রেখে গেছেন তা শব্দের ওজনে পরিমাপ করে বলা যাবে না। ক্রমাগত ৬৭ বছর গভীর নিমগ্নতায় পবিত্র কুরআন মজীদের খেদমতে তিনি যে বিস্ময়কর অবদান রেখে গেছেন, স্মরণকালের ইতিহাসে এর অপর দৃষ্টান্ত বিরল। কুরআনের খেদমতের এই সুদীর্ঘ বর্ণাঢ্য জীবনে তিনি হাজার হাজার হাফেযে কুরআন তৈরি করে গেছেন। তাঁর হাতে গড়া হাফেয-যারা বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিক্ষকতার মাধ্যমে কুরআনের খেদমতে নিয়োজিত আছেন, তাদের সংখ্যাই অর্ধ সহস্রাধিক। মরহুম হাফেয আবদুল হক ছাহেবের কর্মজীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, তিনি শুধু গওহরডাঙ্গা মাদরাসাতেই ক্রমাগতভাবে ৫৮ বছর কুরআনের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর স্মরণকালের ইতিহাসে কুরআনের খেদমতে যুগপৎ ৬৭ বছরের শিক্ষকতা এবং একই প্রতিষ্ঠানে একাধারে ৫৮ বছর শিক্ষক হিসেবে কর্মরত থাকার যে রেকর্ড তিনি সৃষ্টি করেছেন তার অপর কোন দৃষ্টান্ত আজও স্থাপিত হয়নি। প্রাচীন বঙ্গদেশে কুরআনের শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে যারা বিশেষভাবে অবদান রেখে গেছেন তাঁদের মধ্যে হযরত নূর কুতবে আলম রহ. ও হযরত মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরী রহ.-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক সিপাহী বিপ্লবের পর ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী এই অঞ্চল হতে মুসলমানদের নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে ফেলার চেষ্টা করেছিল। ইসলামের সেই কঠিন দুর্দিনে হযরত জৈনপুরী রহ. বাংলার ঘরে ঘরে কুরআনের আলো বিতরণের জেহাদে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। তৎকালে তাঁর প্রচেষ্টায় আরবের মক্কা নগরী হতে বেশ কয়েকজন মুআল্লিম এদেশে আগমন করে কুরআনের শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন। বঙ্গদেশে কুরআনের শিক্ষা বিস্তারের এ ধারাবাহিকতায় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ঢাকার বংশালে একটি আবাসিক হেফয খানা স্থাপিত হয়। প্রাথমিক অবস্থায় প্রায় এক দশক পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি নানা সমস্যার কারণে মন্থর গতিতে অগ্রসর হতে থাকে। পরবর্তীতে চল্লিশ দশকের গোড়ার দিকে নোয়াখালীর প্রখ্যাত হাফেযে কুরআন জনাব আবদুল কাদির ছাহেব মাদরাসাটির দায়িত্ব গ্রহণ করলে এর লেখাপড়ায় গতি সঞ্চারিত হয় এবং তৎকালে তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ঢাকায় হেফয চর্চার ভিত্তি স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে কুমিল্লার ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়া, ফরিদপুরের মুলফৎগঞ্জ ও ঢাকার মির্জাপুরসহ দেশের আরো কয়েকটি জেলায় হেফয খানা প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য তখনো পর্যন্ত এদেশে হেফয পাঠদানের সুনির্দিষ্ট ও প্রাতিষ্ঠানিক কোনো পদ্ধতি গড়ে ওঠেনি। পরবর্তীতে মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর শিক্ষাজীবন শেষ করে ভারত থেকে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর চতুর্দশ শতাব্দীতে হেফয পাঠদানের একটি পূর্ণাঙ্গ ও প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। বর্তমানে বাংলাদেশের অধিকাংশ হেফয খানাগুলোতে এমনকি ভারত ও পাকিস্তানের বহু হেফয খানায় যেই সফল পাঠদান পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে এর উদ্ভাবক মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর রহ.। বর্তমান বাংলাদেশে কুরআন চর্চা ও হেফয শিক্ষার যে উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হচ্ছে এর সূচনা হয়েছিল পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকে। তৎকালে যে কয়জন প্রতিভাবান ও নিবেদিতপ্রাণ হাফেয শিক্ষক কুরআনের খেদমতে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছিলেন এবং যাঁদের অপরিসীম ত্যাগ ও কুরবানীর ফলে বাংলাদেশ পৃথিবীর সর্বাধিক হাফেযের দেশে পরিণত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে তাঁদের অগ্রভাগে ছিলেন-নোয়াখালীর হাফেয আবদুল কাদির রহ, চট্টগ্রামের হাফেয মীর আহমদ রহ., চাঁদপুর শাহতলীর হাফেয মুহসিন রহ., নোয়াখালী নিবাসী ঢাকা লালবাগ মাদরাসার হাফেয মুফিজুর রহমান রহ., ফরিদপুর নিবাসী ঢাকা মিরপুর আরজাবাদ মাদরাসার হাফেয ফয়জুর রহমান রহ. এবং আলোচ্য হাফেয আবদুল হক রহ. ছাহেব প্রমুখ। হাফেয আবদুল কাদির ছাহেব সম্পর্কে যতদূর জানা যায়, শিক্ষক-জীবনের শুরুর দিকে নোয়াখালীতে কয়েক বছর কাজ করার পর তিনি ঢাকা বংশাল মাদরাসায় এসে ক্রমাগত এক যুগেরও অধিককাল কুরআনের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, তৎকালে এতদাঞ্চলে যেমন হেফয খানার সংখ্যা ছিল কম এবং সেই নগণ্য সংখ্যক হেফয খানাগুলোর ছাত্র সংখ্যাও ছিল বর্তমানের তুলনায় অনুল্লেখ্য। সুতরাং সঙ্গত কারণেই তৎকালে হেফয বিভাগে দেশখ্যাত শিক্ষকগণের হাতে গড়া হাফেযদের সংখ্যাও ছিল তুলনামূলক কম। চাঁদপুরের হাফেয মুহসিন ছাহেব পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকার অদূরে মোস্তফাগঞ্জ মাদরাসার হেফয বিভাগে প্রায় ১৬ বছর কর্মরত ছিলেন। হাফেয মুহসিন ছাহেব হেফয বিভাগের পাশাপাশি কিতাব বিভাগে শিক্ষকতা করলেও সেই সময়ে তিনি হাফেয গড়ার একজন সুদক্ষ শিক্ষক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৯৬৪ সালে তিনি চাঁদপুরের নিজ নিবাস মুমিনপুরে একটি আদর্শ হেফয খানা গড়ে তোলেন। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি সেখানেই কর্মরত ছিলেন। নোয়াখালী নিবাসী হাফেয মুফিজুর রহমান ছাহেব ছিলেন ঢাকা লালবাগ মাদরাসার হেফয বিভাগের প্রধান শিক্ষক। অত্র মাদরাসার প্রতিষ্ঠাকাল (১৯৫০) হতেই হযরত হাফেজ্জী হুজুর তাকে এই দায়িত্বে নিয়োগ দেন। ১৯৬৭ সালে ইন্তেকালের সময় পর্যন্ত ক্রমাগত ১৮ বছর তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সাথে এই দায়িত্ব পালন করেন। লালবাগ মাদরাসায় যোগদানের পূর্বে তিনি ঢাকা বড় কাটারা মাদরাসার হেফয বিভাগে ৪ বছর কর্মরত ছিলেন। সে মতে শিক্ষক জীবনের সুদীর্ঘ ২২ বছরে তিনি অসংখ্য হাফেযে কুরআন তৈরি করে গেছেন। চট্টগ্রামের হাফেয মীর আহমদ ছাহেব ছিলেন গওহরডাঙ্গা মাদরাসার হেফয বিভাগের প্রথম শিক্ষক। সেখানে কয়েক বছর কাজ করার পর তিনি ঢাকা মোমেন মটর কোম্পানি মাদরাসায় চলে আসেন। এখানে কয়েক বছর কাজ করার পর ঢাকাসহ সমগ্র দেশে একজন সুদক্ষ শিক্ষক হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে তিনি সৌদী আরব চলে যান এবং সেখানেই তাঁর ইন্তেকাল হয়। বাংলাদেশে যে কয়জন প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব আল কুরআনের খেদমত তথা হাফেয গড়ার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন, মরহুম হাফেয ফয়জুর রহমান ছিলেন তাঁদের অন্যতম। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ঢাকা মোস্তফাগঞ্জ, নরসিংহপুর, ফরিদাবাদ, মিরপুর, আমীনবাজার, আরজাবাদ ও মোমেন মটর কোম্পানি মাদরাসায় প্রায় অর্ধশতাব্দীর শিক্ষকজীবনে তিনি সহস্রাধিক হাফেয তৈরি করে গেছেন। এরপরই আসে আমাদের আলোচ্য হাফেয আবদুল হক ছাহেব প্রসঙ্গ। গওহরডাঙ্গা মাদরাসার হেফয বিভাগের প্রধান শিক্ষক মরহুম হাফেয আবদুল হক ছাহেব তাঁর শিষ্য-শাগরিদ ও পরিচিত পরিমন্ডলে ‘বড় হুজুর’ নামেই খ্যাত ছিলেন। ১৯২৭ সালের ২ মার্চ চাঁদপুর জেলার মতলব থানাধীন ধলাইতলী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত দ্বীনী পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জনাব আবদুল আজীজ দরবেশ ছিলেন উজানীর ক্বারী ইবরাহীম ছাহেবের খাছ শিষ্য। তৎকালে নিজের এলাকায় তিনি একজন সহজ-সরল ধার্মিক ব্যক্তি হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বালক আবদুল হক স্থানীয় মকতব ও পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর পবিত্র কুরআন হেফয করার উদ্দেশ্যে পার্শ্ববর্তী করদী গ্রামে চলে যান। সেখানে হাফেয মাওলানা আবদুল মজীদ নামে এক বুযুর্গ নিজের বাড়িতে স্বল্প পরিসরে একটি হেফয খানা চালু করেছিলেন। ‘করদীর হুজুর’ নামে খ্যাত এই বুযুর্গ ছিলেন হযরত হাফেজ্জী হুজুরের বিশিষ্ট খলীফা। প্রচন্ড মেধার অধিকারী কিশোর আবদুল হক করদীর হুজুরের বিশেষ তত্ত্বাবধানে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে যথাসময়ে হেফয সম্পন্ন করেন। অতঃপর ফরিদগঞ্জ থানার শাসিয়ালীতে এক কওমী মাদরাসায় কিতাব বিভাগের মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর পারিপার্শ্বিক নানা সমস্যার কারণে তাঁর পক্ষে আর উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। অতঃপর সেই যুবা বয়সেই তিনি পার্শ্ববর্তী জাফরাবাদ মাদরাসার হেফয বিভাগে শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। এদিকে জাফরাবাদ মাদরাসায় শিক্ষকতার সূচনাকাল হতেই তিনি নিজের এছলাহ ও আত্মসংশোধনের উদ্দেশ্যে হযরত হাফেজ্জী হুজুরের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। সেই সূত্রেই বছরে অন্তত কয়েকবার ঢাকা লালবাগ মাদরাসায় এসে তিনি হযরত হাফেজ্জী হুজুরের সঙ্গে সাক্ষাত করতেন। ১৯৫২ সালের কথা। মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর ও মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (ছদর ছাহেব হুজুর) সদ্য প্রতিষ্ঠিত লালবাগ মাদরাসা নিয়ে ব্যস্ত। এদিকে হযরত ছদর ছাহেব হুজুর ইতিপূর্বেই নিজ নিবাস ফরিদপুর জেলার গওহরডাঙ্গায় ‘দারুল উলূম খাদেমুল ইসলাম’ নামে একটি বৃহত্তম মাদরাসা গড়ে তুলেছেন। এই সময় ছদর ছাহেব হুজুর গওহরডাঙ্গা মাদরাসার হেফয বিভাগের জন্য একজন দক্ষ শিক্ষক সন্ধান করছিলেন। পরে এই বিষয়ে তিনি হযরত হাফেজ্জী হুজুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এদিকে হাফেয আবদুল হক ছাহেব তখন কুমিল্লা জাফরাবাদ মাদরাসায় দীর্ঘ নয় বছর শিক্ষকতা করার পর প্রাতিষ্ঠানিক কিছু জটিলতার কারণে ওই মাদরাসা হতে অব্যাহতি গ্রহণ করেন। এর কিছুদিন পরই তিনি ঢাকায় গিয়ে পরবর্তী করণীয় বিষয়ে নিজের শায়খ ও মুরববী হযরত হাফেজ্জী হুজুরের পরামর্শ প্রার্থনা করেন। হাফেজ্জী হুজুর সকল দিক বিবেচনা করে তাকে গওহরডাঙ্গা মাদরাসার হেফয বিভাগে যোগদানের পরামর্শ দেন। হুজুরের এই পরামর্শের সঙ্গে সঙ্গেই হাফেয আবদুল হক ছাহেব মানসিকভাবে গওহরডাঙ্গা মাদরাসায় যাওয়ার স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন। উপরোক্ত সিদ্ধান্তের পর হাফেয আবদুল হক ছাহেব দেশের বাড়ি চাঁদপুরে ফিরে এসে পরিবারের মুরববীগণকে এই সিদ্ধান্তের কথা অবহিত করেন এবং যথাসময়ে গওহরডাঙ্গা যাওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে ঢাকা লালবাগ মাদরাসায় এসে উপস্থিত হন। হাফেজ্জী হুজুরের সঙ্গে সাক্ষাত হওয়ার পর হুজুর তাকে বললেন, ‘তুমি আপাতত আমার এখানে কয়েকদিন থাক। আমাকে পূর্ণ এক খতম কুরআন শুনিয়ে তবে গওহরডাঙ্গা যাবে।’ হাফেজ্জী হুজুরের উপরোক্ত প্রস্তাবে হাফেয আবদুল হক ছাহেব যারপরনাই আনন্দিত হয়ে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করলেন। কারণ, তিনি কল্পনাও করতে পারেননি যে, আল্লাহ তাআলা তাকে এমন বিরল সৌভাগ্য লাভের সুযোগ করে দিবেন। যাই হোক, অল্প কয়েকদিনে হাফেজ্জী হুজুরকে খতম শোনানো শেষ হওয়ার পর হুজুর তাঁর জন্য দুআ করলেন যেন আল্লাহ পাক তাঁর দ্বারা কুরআনের খেদমত নেন। ১৯৫২ সালের জুন মাস। হাফেয আবদুল হক ছাহেব আল্লাহর পবিত্র কালামের খেদমত করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ফরিদপুর জেলার অর্ন্তগত গওহরডাঙ্গা মাদরাসায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে বহন করে নিয়ে এলেন মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা আবদুল আজীজ ছাহেবকে লেখা হযরত ছদর ছাহেব হুজুরের চিঠি। ওই একই চিঠির নীচের অংশে হযরত হাফেজ্জী হুজুর সংক্ষেপে লিখে দিলেন, ... ‘আমি আশা করিতেছি, পত্রবাহক হাফেয আবদুল হক ছাহেব হযরত ছদর ছাহেবের মানশা অনুযায়ী কুরআনের খেদমত করিতে পারিবেন। আল্লাহ পাক তাহার অন্তরে এখলাস দান করুন এবং তা-হায়াত (আজীবন) খেদমত করার তাওফীক দান করুন।’ গওহরডাঙ্গা মাদরাসায় আসার পর হাফেয আবদুল হক ছাহেব নতুন পরিবেশে নব উদ্যমে কাজ শুরু করলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি বহুবার বলেছেন, ‘হাফেজ্জী হুজুরের সেদিনের সেই দুআ ছিল আমার কর্মজীবনে প্রেরণার উৎস, আমার জীবন-পথের আলোকবর্তিকা।’ যাই হোক, গওহরডাঙ্গা মাদরাসার হেফয বিভাগটি তখন খুবই অগোছালো ছিল। কিন্তু হুজুরের নিপুণ কর্মদক্ষতায় অল্প দিনেই এই বিভাগটির সার্বিক শৃঙ্খলা ফিরে আসে এবং দিনে দিনে এর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে কয়েক মাসের মধ্যেই আশাতীতভাবে ছাত্র-সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আসলে গওহরডাঙ্গা মাদরাসার যা কিছু সুনাম-সুখ্যাতি তার প্রায় সবটুকু এই হেফয খানাকে কেন্দ্র করেই। বড় হুজুরের এখলাস-আন্তরিকতা ও গতিশীল নেতৃত্বের ফলে ষাট দশকের মাঝামাঝি সময়ে এসে গওহরডাঙ্গা মাদরাসার হেফয বিভাগটি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম শীর্ষ হেফয খানায় পরিণত হয় এবং হুজুরের ইন্তেকাল পর্যন্ত সাফল্যের এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। কর্তব্য-কাজে স্থিরতা ও নিমগ্নতায় তিনি ছিলেন এক অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। যুবা বয়সে (১৯৫২ সালে) সেই যে বাড়ি হতে বের হয়ে আসলেন অতঃপর আর পিছনের দিকে ফিরে দেখার অবসর পাননি। অন্তহীন প্রতিকূলতা ও পর্বতপরিমাণ সমস্যা উপেক্ষা করে তিনি পথ চলেছেন অবিরাম। এ পথ চলায় তিনি ছিলেন অবিচল-ক্লান্তিহীন পারিপার্শ্বিক কোন সংকটই তাঁর যাত্রা পথে অন্তরায় হতে পারেনি। হেরার আলো বিতরণের এ মহান অভিযাত্রায় প্রতি বছরই তিনি জাতিকে একদল সুদক্ষ হাফেয উপহার দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনের এ মহান সেবক সুদীর্ঘ ৬৭ বছর শিক্ষকজীবনে বহু হাফেয তৈরি করেছেন। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী তাঁর নিকট হেফয সম্পন্ন করেছেন এমন প্রায় সাড়ে তিন হাজার হাফেযের মাথায় তিনি পাগড়ি পরিয়েছেন। যারা আংশিক পড়েছেন অর্থাৎ তাঁর নিকট হেফয শেষ না করার কারণে যাদেরকে তিনি পাগড়ি দেননি তাদের সংখ্যা প্রায় পনের সহস্রাধিক। বড় হুজুরের জীবনের শ্রেষ্ঠ সাফল্য-স্মরণকালের ইতিহাসে তাঁর হাতেই সর্বাধিক সংখ্যক ‘খাদেমুল কুরআন’ বা হেফয খানার শিক্ষক তৈরি হয়েছে। ফরিদপুর, খুলনা, যশোহর ও বরিশাল জেলার অধিকাংশ হেফয খানাসহ বাংলাদেশের প্রায় সকল অঞ্চলের হেফয খানাগুলোতে তাঁর শিষ্যগণ হেফযে কুরআনের মহান খেদমতে নিয়োজিত আছেন। সম্প্রতি পরিচালিত এক আঞ্চলিক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বড় হুজুরের হাতে গড়া ৬২ জন হাফেয শুধু ঢাকা ও তৎসংলগ্ন এলাকার বিভিন্ন হেফয খানায় শিক্ষকরূপে কর্মরত আছেন। হেফয শেষ করার পর দাওরায়ে হাদীস পাশ করে কিতাব বিভাগে শিক্ষকতা করছেন এমন হাফেযদের সংখ্যা ৩৩। ওই একই অঞ্চলের বিভিন্ন মসজিদে ইমাম-খতীব হিসেবে যারা খেদমত করছেন তাদের সংখ্যা ২৭। অর্থাৎ শুধু বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলেই প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী হুজুরের হাতে গড়া ১২৬ জন হাফেয বিভিন্ন মাদরাসা-মসজিদের খেদমতে নিয়োজিত আছেন। এ হল দেশের একটি খন্ড চিত্র। আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি-দক্ষিণ বঙ্গের চারটি জেলাতেই হুজুরের ছাত্র সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সুতরাং জেলাওয়ারী পরিসংখ্যান তৈরি করলে ওই চার জেলাই শীর্ষে থাকবে। তাছাড়া ভারত, পাকিস্তান, বৃটেন, আমেরিকা এবং কাতার, বাহরাইন ও কুয়েতসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশে দেশে হুজুরের অনেক ছাত্র বিভিন্ন হেফয খানায় শিক্ষকতা ও মসজিদের ইমাম হিসেবে কর্মরত আছেন। হুজুরের ছাত্র ঢাকা কামরাঙ্গীরচরের হাফেয ফরিদ পাকিস্তানের করাচিতে একটি উন্নতমানের হেফয খানা স্থাপন করে বেশ সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। হাফেয ফরিদ সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ ঘটনা আছে। ১৯৭৮-৭৯ সালে তিনি ঢাকা কামরাঙ্গীরচর নূরিয়া মাদরাসায় হেফয বিভাগের ছাত্র ছিলেন। ক্রমাগত কয়েক বছর তার হেফয পড়ায় কোনো অগ্রগতি না হওয়ায় তৎকালীন নূরিয়ার মুহতামিম ও হেফয বিভাগের প্রধান শিক্ষক ফরিদকে হেফয পড়ার অযোগ্য ঘোষণা করেন। এই অপ্রত্যাশিত ঘোষণা শোনার পর ফরিদ ও তার পিতামাতা হতাশায় মুষড়ে পড়েন। আমি (লেখক) তখন হেফয খানার শিক্ষক। একপর্যায়ে ফরিদের পিতা এ বিষয়ে আমার পরামর্শ চাইলে আমি প্রথমত সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে ফরিদ ও তার পিতামাতাকে কিছুটা আশাবাদী করে তোলার পর ফরিদকে গওহরডাঙ্গা মাদরাসায় পাঠিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেই। সেমতে ফরিদের পিতা কালবিলম্ব না করে তাকে গওহরডাঙ্গা মাদরাসায় নিয়ে যান। ফরিদের সঙ্গে প্রদত্ত বড় হুজুরকে লেখা এক চিঠিতে আমি অনুরোধ করেছিলাম ....‘ফরিদ সম্পর্কে লিখিত ঘোষণায় বলা হয়েছে, সে কখনো হাফেয হতে পারবে না। এই ঘোষণার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে আমি তাকে আপনার খেদমতে হাজির হওয়ার পরামর্শ দিয়েছি ...।’ পরে শুনেছি, বড় হুজুর আমার পত্র পাঠ করে জোশের সাথে ফরিদকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, ‘ফরিদ! কে বলেছে তুমি হাফেয হতে পারবে না। ইনশাআল্লাহ তুমি হাফেয হবে এবং নূরিয়ার হেফয খানার প্রধান শিক্ষক হবে।’ আল্লাহু আকবার! সেই ফরিদ, হাফেয হওয়ার অযোগ্য (?) ফরিদ, ১৯৯২ সালে নূরিয়ার হেফয বিভাগের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যাই হোক, বড় হুজুরের শিক্ষাদান পদ্ধতি কি ছিল এবং এই ক্ষেত্রে তিনি কি কি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন তা এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। শিক্ষকজীবনে তাঁর সাফল্যের মূলে ছিল-এখলাছ ও লিল্লাহিয়াত। সারাদিন ছাত্রদের পিছনে মেহনত করার পর রাতের গভীরে নফল নামায পড়ে তিনি আল্লাহর দরবারে কেঁদে কেঁদে ছাত্রদের উন্নতি ও তরক্কীর জন্য দুআ করতেন। হেফয শিক্ষাদানের গতানুগতিক কোনো নিয়ম বা একক কোনো পদ্ধতিতে তিনি পড়াতেন না; বরং প্রতিটি ছাত্রকে নিয়ে তিনি পৃথকভাবে চিন্তা করতেন। শাসন, সোহাগ ও উদ্বুদ্ধ করণ-এই তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে এক ভারসাম্যপূর্ণ ও সমন্বিত পদ্ধতিতে তিনি শিক্ষাদান করতেন। শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা, মানসিক অবস্থা ও পারিবারিক অবস্থান ইত্যাদি বিষয়গুলোকে সামনে রেখে তা’লীম ও তরবিয়তের অবকাঠামো গড়ে তুলতেন। প্রতিনিয়ত ছাত্রদের অবস্থা নিয়ে গবেষণা করতেন এবং চলমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিত্য নতুন কৌশল অবলম্বন করতেন এবং প্রয়োজনে তা পরিবর্তনও করতেন। হুজুরের নিয়ম ছিল, প্রতিদিনের সবক নির্ভুল হলে নির্দিষ্ট অঙ্কের পয়সা পুরস্কার দিতেন। প্রতিদিনের এই পয়সা খাতায় লেখা থাকত এবং মাস শেষে তা ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করা হত। আর প্রতিযোগিতামূলক সবিনাগুলোতে নির্ভুল পারা পড়তে পারলে আকর্ষণীয় পুরস্কার দেওয়া হত। অর্থাৎ এই ভাবেই তিনি ছাত্রদেরকে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবে উজ্জীবিত করে এবং আনন্দ, ফূর্তিতে মাতিয়ে রেখে তাদের পড়া আদায় করতেন। নিজের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলতেন, ‘ক্রমাগত শাসনের জোয়ালে আটকে রেখে পড়া আদায় করার যে চেষ্টা করা হয় তা ফলপ্রসু নয়। পড়ার প্রতি ছাত্রদের এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে যেন অত:পর তারা স্বেচ্ছায় কোরআনের জন্য পাগলপারা হয়ে মেহনত করতে থাকে।’ হুজুর বলতেন, ‘মেধাহীন, এতীম-গরীব, অসহায় এবং চঞ্চল-ডানপিটে ও প্রত্যাখ্যাত ছেলেরাই আমার প্রিয় ছাত্র। এদের পিছনে মেহনত করতে আমি অধিক উৎসাহ বোধ করি। কেননা, ভবিষ্যতে এই গরিব-গোরাবাদের দ্বারাই দ্বীনের খেদমত তুলনামূলক বেশি হবে বলে আশা করা যায়।’ ছাত্রদের উৎসাহ বৃদ্ধি ও তাদের মনোবল চাঙ্গা করার উদ্দেশ্যে হুজুর মাঝেমধ্যেই সকলকে জড়ো করে উৎসাহব্যঞ্জক বক্তব্য রাখতেন। ... প্রখ্যাত হাফেযগণ পাঠ্যজীবনে কেমন করে মেহনত করেছেন, কঠিন প্রতিকূলতার ভিতরও একজন কুরআন পিপাসুকে কেমন করে সাধনা করতে হয় ইত্যাদি বিষয়গুলো হুজুর এমনভাবে তুলে ধরতেন, যা শুনে ছাত্রদের ধমনীতে রক্ত টগবগ করে উঠত। হুজুরের এই জাতীয় বক্তব্য শুনে নেহায়েত অমনোযোগী ছাত্ররাও বিপুল উদ্দীপনায় কুরআনের জন্য পাগলপারা হয়ে মেহনত শুরু করে দিত। বড় হুজুরের এই কৌশলের ফলেই দেখা গেছে, দিনের পর দিন ক্রমাগতভাবে হেফয খানার অধিকাংশ ছাত্র সমস্ত রাত্রি জেগে জেগে কুরআন তেলাওয়াত করেছে। আমার (লেখক) সহপাঠী খুলনার হাফেয আবদুল মান্নান প্রতিদিন এক খতম তেলাওয়াত করতেন। সম্প্রতি আমার হেফয খানায় ছাত্রদের মজলিসে তিনি নিজের ছাত্রজীবনের স্মৃতিচারণ করে বলেছিলেন ... ‘গওহরডাঙ্গা মাদরাসায় আমার পাঠ্য জীবনের (১৯৭২-৭৪) কথা। আমি যেদিন সবচেয়ে কম তেলাওয়াত করেছি সেদিন ২৫ পারা তেলাওয়াত করেছিলাম।’ পরবর্তীতে এই হাফেয আবদুল মান্নান পাকিস্তানের করাচি শহরে ‘ইকরা রওজাতুল আতফাল’ এবং আল-হেরা একাডেমীর হেফয খানায় নয় বছর কুরআনের খেদমত করেছেন। মরহুম বড় হুজুর গওহরডাঙ্গা হেফয খানায় যে পরিবেশ সৃষ্টি করে গেছেন, উপমহাদেশের অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে এর নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না। ... গভীর রাতে পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়ার পর গওহরডাঙ্গা মাদরাসার আশেপাশে গেলে শোনা যাবে, রাতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে চতুর্দিক হতে কুরআন তেলাওয়াতের সুমধুর আওয়াজ ভেসে আসছে। মসজিদের ছাদ, নদীর তীর, নির্জন বৃক্ষতল, বিজন কবরস্থান ইত্যাদি অঙ্গনে বসে হেফয খানার কুরআন পিপাসুগণ সারারাত কুরআন তেলাওয়াত করছে। এ দৃশ্য বর্ষব্যাপী-নিত্যদিনের। এই পরিবেশ কি এমনি হয়েছে? বাংলাদেশে প্রাজ্ঞ হাফেয তৈরি এবং বিশেষত হেফয খানার শিক্ষক তৈরির ক্ষেত্রে গওহরডাঙ্গা হেফয খানার অবদান সর্বশীর্ষে-এ কথা আজ সকল বিতর্কের উর্ধ্বে। অথচ যার বিপুল সাধনার সৃষ্টি এ ফসল, তিনি কিন্তু মনেও করতেন না এ কীর্তির পিছনে তাঁর কোনো অবদান আছে। তিনি কখনো বলতেন না, ‘আমার ছাত্র বা আমার হাফেয’; বরং এ প্রসঙ্গে সব সময় তাঁর উক্তি ছিল, ‘গওহরডাঙ্গা হেফয খানার ছাত্র।’ তাঁর যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বের বড় প্রমাণ, তিনি সত্যিকার অর্থেই নিজেকে একজন ‘অযোগ্য’ মনে করতেন। পরম দায়িত্ববোধ ও গভীর নিমগ্নতায় তিনি ছাত্রদের পিছনে মেহনত করতেন। আলস্য কিংবা সময়ের অপচয় তাঁকে কখনো স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁর হেফয খানায় বরাবরই ছাত্রসংখ্যা ছিল বিপুল। তিনি একাই প্রায় একশত ছাত্র পড়াতেন। আজ হতে প্রায় চার দশক পূর্বে আমি (লেখক) যখন গওহরডাঙ্গা হেফয খানায় পড়ি তখন হুজুরের জামায়াতে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১০২ জন। গওহরডাঙ্গা হেফয খানার সঙ্গে যারা পরিচিত নয় তাদের নিকট এ তথ্যটি অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে বটে। আসলে অনেক অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব বিষয় তাঁর দ্বারা বাস্তবে সম্ভব হয়েছে বলেই এ অঙ্গনে তিনি ছিলেন সকলের শীর্ষে। হুজুর একসঙ্গে একাধিক ছাত্রের পড়া শুনতেন। অবশ্য এ কারণে ছাত্রদের পড়ায় ত্রুটি থেকে যেত-এমন মনে করার কোনো কারণ ছিল না। বহুজন বহুভাবে পরীক্ষা করেই এ সত্যের প্রমাণ পেয়েছেন। অর্থাৎ বড় হুজুর এমনই হুশিয়ার ও বিচক্ষণ ছিলেন যে, কয়েকজনের পড়া একসঙ্গে শুনলেও কারো কোনো ভুল ছুটে যেত না। এ প্রসঙ্গে হযরত হাফেজ্জী হুজুরের একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য হল, ‘হাফেয আবদুল হক ছাহেব যখন একসঙ্গে কয়েকজনের পড়া শুনতেন তখন অবস্থা দেখে মনে হয়েছে, যেন শুধুমাত্র ভুল পড়াগুলোই তার কানে প্রবেশ করছে এবং নির্ভুল ও শুদ্ধ পড়াগুলো তিনি শুনতেই পাচ্ছেন না।’ হাফেজ্জী হুজুরের ছোট ছেলে মাওলানা আতাউল্লাহ শৈশবে খুবই চঞ্চল প্রকৃতির ছিলেন। রাজধানী ঢাকায় রেখে যখন কিছুতেই তার পড়ায় অগ্রগতি হচ্ছিল না, তখন হাফেজ্জী হুজুর অত্যন্ত নির্ভরতার সাথে তাকে গওহরডাঙ্গা হেফয খানার বড় হুজুরের হাতে তুলে দেন। ৩ বছর পর সেই আতাউল্লাহ যখন ঢাকায় ফিরে এসে লালবাগ শাহী মসজিদে খতমে তারাবীহ পড়ান, তখন তার উচ্চমার্গীয় তেলাওয়াত শোনার জন্য রাজধানীর অসংখ্য হাফেয-আলেম এসে তাঁর পিছনে ইকতিদা করতেন। আমাদের দেশে অনেক বড় বড় আলেম ও পীর-বুযুর্গের সন্তানদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হওয়ার অন্যতম কারণ হল, তাদেরকে সাধারণ ছাত্র হিসেবে গ্রহণ না করে ‘ছাহেবজাদা’র মর্যাদায় (?) গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আমাদের বড় হুজুর ছিলেন এর ব্যতিক্রম। এ কারণেই দেখা যায়, হাফেজ্জী হুজুর, ছদর ছাহেব হুজুরসহ দেশের অনেক বরেণ্য আলেমের সন্তানগণ তাঁর হাতে মানুষ হয়েছেন। আসলে বড় হুজুরের শিক্ষকজীবনের সাফল্যের চাবিকাঠি ছিল তাঁর এখলাছ, আন্তরিকতা ও আধ্যাত্মিক বুযুর্গী। তিনি যা করতেন তা আল্লাহ পাকের রেজা ও সন্তুষ্টির জন্যই করতেন। প্রতিদিন এশার নামাযান্তে ছুটির পর ছাত্রদের জড়ো করে দুরূদ-ইস্তেগফার পাঠের পর তিনি দোয়া করতেন। প্রতিদিনের এই সম্মিলিত দোয়ায় তিনি বিশেষভাবে নিজের অযোগ্যতা-অক্ষমতা প্রকাশ করে ছাত্রদের এলমী-আমলী এছলাহ ও তরক্কীর জন্য রাববুল আলামীনের সাহায্য প্রার্থনা করতেন। তাছাড়া প্রয়াত আকাবিরে দ্বীন এবং উপস্থিত সকলের মৃত আত্মীয়-স্বজনসহ সমস্ত উম্মতে মোহাম্মদীর গোনাহ-খাতা মাফী ও দ্বীন-দুনিয়ার ভালাই কামনা করে কায়মনোবাক্যে দোয়া করতেন। এই আমলটি তিনি নিয়মিত করতেন। হুজুর ছিলেন প্রচারবিমুখ এক নিরিবিলি চরিত্রের মানুষ। মানুষের নিকট তাঁর কোনো কাজের প্রচার-প্রশংসা হতে পারে এমনসব কর্মকান্ডকে তিনি যত্নের সঙ্গে এড়িয়ে চলেছেন। হযরত হাফেজ্জী হুজুর ও ছদর ছাহেব হুজুরের সংসর্গ লাভে ধন্য এ মহাপুরুষ কি পরিমাণ বুযুর্গীর অধিকারী ছিলেন তা অল্প কথায় প্রকাশ করা যাবে না। দিনরাত অবিরাম কুরআনের পিছনে অন্তহীন মেহনত করার পরও তিনি প্রচুর নফল এবাদত করতেন। জীবনে তিনি দুইবার (১৯৬৮-১৯৯৮) হজ্ব করেছেন। নিয়মিত প্রায় একশত ছাত্রের সবক-আমুখতা (পিছনের পড়া) শুনতে সমস্ত দিন তাঁকে অবিশ্রান্ত মেহনত করতে হত। অথচ রাতেও তিনি খুব বেশি বিশ্রাম গ্রহণ করতেন না। অর্ধরাতের পর উঠে নফল নামাযে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কুরআন তেলাওয়াত করতেন। নামাযে ক্লান্তি আসলে বসে জিকির করতেন। হেফয খানার বারান্দায় একটি খাট পাতা ছিল। ওই খাটের উপরই তিনি রাতের ইবাদতে মশগুলে হতেন। ছাত্রাবস্থায় কিছুদিন হুজুরের খেদমত করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। রাতে তাহাজ্জুদের সময় হুজুরের অযু-ইস্তেঞ্জার যোগান দেওয়ার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। তাহাজ্জুদ শেষে তিনি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মুনাজাত করতেন। সেই মুনাজাতে নিজের কথা খুব কমই বলতেন। তাঁর সমস্ত মুনাজাত জুড়ে থাকত নিজের রূহানী সন্তানদের ইলমী-আমলী তরক্কীর নিবেদন। আমি অনেকদিন হুজুরের সেই খাট সংলগ্ন (হেফয খানার অভ্যন্তর অংশে) বসে হুজুরের মুনাজাত শুনেছি। যে কথাটি তিনি প্রায় সকল মুনাজাতেই বলতেন তা হল, ‘ইয়া আল্লাহ! আমাকে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত কুরআনের খেদমত করে যাওয়ার তাওফীক দান করিও।’ আল্লাহ তাঁর কোন বান্দাকেই নিরাশ করেন না। হুজুরের সারা জীবনের এই বাসনাও আল্লাহ পূরণ করেছেন। কুরআনের খেদমতরত অবস্থায় তিনি রফীকে আ’লার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। ইন্তেকালের সময় তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে ও চার কন্যাসন্তান রেখে গেছেন। ছেলেমেয়ে সকলেরই বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে এবং হুজুরের তিন ছেলেই কুরআনের খেদমতে নিয়োজিত আছেন। পৃথিবীর সকলকেই একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে। কিন্তু মৃত্যুর পরও কিছু মানুষ অমর হয়ে থাকে তার কর্ম ও কীর্তির মাঝে। আমাদের বড় হুজুরের কীর্তি বিশাল-বিস্তৃত। তিনি যুগ-যুগান্তরে অমর হয়ে থাকবেন তাঁর অসংখ্য হাফেযের মাঝে, দেশ-দেশান্তরে। আল্লাহ পাক তাঁকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন। #