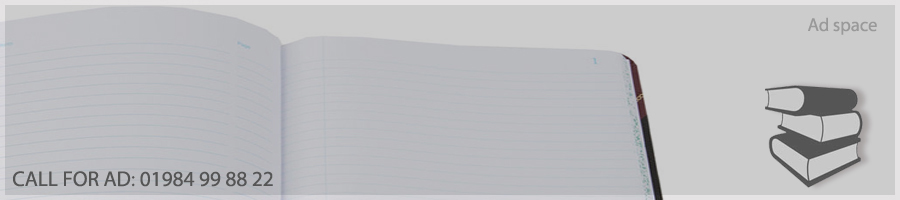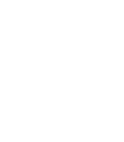মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ঐক্য সৃষ্টির চেষ্টা করুন একই দিনে ঈদের বিষয় দায়িত্বশীলদের উপর ছাড়ুন-৫
শাফেয়ী মাযহাব
আলোচিত মাসআলায় হানাফী মাযহাবের ফকীহগণের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কিছু আলোচনা হয়েছে। আরো কিছু কথা সামনের শিরোনামগুলোর অধীনেও হবে ইনশাআল্লাহ। এখন অন্য তিন মাযহাবের (শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী) ফকীহগণের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা মুনাসিব মনে হচ্ছে।
প্রথমে শাফেয়ী মাযহাব। তবে তা বর্ণনার আগে ভূমিকা হিসেবে এটুকু বলে নিচ্ছি যে, শাফেয়ী মাযহাবের ফিকহের কিতাবগুলোর পরিভাষায় ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর সিদ্ধান্তগুলোকে ‘ক্বওল’ (قول ) ব.ব আকওয়াল (أقوال) বলে। আর মাযহাবের অনুসারী ও ভাষ্যকার ইমামদের ইস্তিমবাতকৃত মতামতকে ‘ওয়াজহ’ (وجه) ব.ব ‘উজূহ’ (وجوه) বলে। ‘আকওয়াল’ বা ‘উজূহ’ বর্ণনার ক্ষেত্রে মাযহাবের ফকীহগণের মাঝে পার্থক্য বা বিভিন্নতা দেখা দিলে একে ‘তরীক’ (طريق) বলে।
শাফেয়ী মাযহাবের বর্ণনা ও উপস্থাপনা এবং ব্যাখ্যা ও দলিল-নির্দেশের ক্ষেত্রে মৌলিকভাবে দুটি বড় ‘তরীকা’ আছে : ‘তরীকাতুল ইরাকিয়ীন’ (ইরাকীগণের তরীকা) ও ‘তরীকাতুল খুরাসানিয়ীন’ (খুরাসানীগণের তরীকা)। প্রথম তরীকার শায়খ (প্রধান) হলেন আবু হামিদ আসফারাইনী (৩৪৪-৪০৬ হি.)। আর দ্বিতীয় তরীকার শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ কাফফাল মারওয়াযী (৪১৭ হি.)। (আলমাজমূ শরহুল মুহাযযাব, ইমাম নববী, ভূমিকা; তবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাতিল কুবরা, তাজুদ্দীন সুবকী ৫/৫৪)
ভূমিকার পর এবার মূল প্রসঙ্গ
শাফেয়ী ফকীহগণ আলোচিত মাসআলায় (এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় কি না) শুধু ‘উজূহ’ বর্ণনা করেছেন, ‘আকওয়াল’ বর্ণনা করেননি। এর অর্থ, তাঁরা এ মাসআলা ইমাম শাফেয়ীর কিতাবসমূহে পাননি এবং ইমাম শাফেয়ী রাহ. থেকে তাদের কাছে এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত পৌঁছেনি। তাঁদের কাছে শুধু আছে ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর অনুসারী ফকীহ ইমামগণের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত।
ইমাম শাফেয়ী রাহ. থেকে এ মাসআলা স্পষ্টভাবে বর্ণিত না হওয়ার এক বড় আলামত এ-ও যে, শাফেয়ী মাযহাবের সবচেয়ে বড় সহায়তাকারী ইমাম বায়হাকী রাহ.-এর কিতাব ‘‘মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আছার’’-এ (যার বিষয়বস্ত্তই হচ্ছে ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর সিদ্ধান্তসমূহের দলিল উল্লেখ করা) আমাদের জানা মতে, এ মাসআলার উল্লেখ নেই। এখন দেখার বিষয় এই যে, শাফেয়ী মাযহাবের অধিকাংশ ফকীহ কোন দিকে। সাইমারী ও আবুত তাইয়েব তবারীসহ কতিপয় মনীষী যদিও বলেন, এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্যও অবশ্যঅনুসরণীয়, কিন্তু অধিকাংশ শাফেয়ী ফকীহর সিদ্ধান্ত এই যে, দূর-দূরান্তের শহর-নগরে এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গার জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় না হওয়াই সঠিক। তবে নিকট ও দূরের মাপকাঠি সম্পর্কে শাফেয়ী ফকীহ ও অন্যান্য ফকীহগণের বিভিন্ন মত আছে। ইনশাআল্লাহ এ বিষয়ে পরে আলাদাভাবে আলোচনা হবে। শাফেয়ী মাযহাবের সর্বসম্মত মুখপাত্র ইমাম আবু যাকারিয়া নববী রাহ. (৬৭৬ হি.) ‘‘শরহুল মুহাযযাবে’’ লেখেন-
إذا رأوا الهلال في رمضان في بلد ولم يروه في غيره، فإن تقارب البلدان فحكمهما حكم بلد واحد ويلزم أهل البلد الآخر الصوم بلا خلاف، وإن تباعدا فوجهان مشهوران في الطريقتين :
أصحهما : لا يجب الصوم على أهل البلد الآخر، وبهذا قطع المصنف والشيخ أبو حامد والبَنْدَنِيْجِي وآخرون، وصححه العَبْدَرِي والرافعي والأكثرون.
والثاني : يجب، وبه قال الصيمري، وصححه القاضي أبو الطيب، والدارمي، وأبو علي السِّنْجِي وغيرهم.
অর্থ, এক শহরের লোকেরা রমযানের চাঁদ দেখেছে, অন্য শহরের লোকেরা দেখেনি এক্ষেত্রে শহর দুটি কাছাকাছি হলে তা এক শহরের মতো গণ্য হবে। সুতরাং দ্বিতীয় শহরের অধিবাসীদেরও রোযা রাখা জরুরি হবে। এতে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু যদি দুই শহর পরস্পর দূরবর্তী হয় তাহলে এক্ষেত্রে দুই ‘তরীকায়’ দুটি প্রসিদ্ধ ‘ওয়াজহ’ রয়েছে : অধিকতর শুদ্ধ ‘ওয়াজহ’ এই যে, (এক শহরে চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার কারণে) অন্য শহরের অধিবাসীদের উপর রোযা রাখা জরুরি হবে না। গ্রন্থকার (আবু ইসহাক শীরাজী), শায়খ আবু হামিদ, বান্দানীজী ও অন্যরা নিশ্চিতভাবে এ কথাই বলেছেন। (অর্থাৎ অন্য মতের উল্লেখও করেননি) আবদারি ও রাফেয়ীসহ অধিকাংশ মনীষী একেই সহীহ বলেছেন।
‘দ্বিতীয় ‘ওয়াজহ’ এই যে, রোযা রাখা জরুরি হবে। সাইমারী তা বলেছেন এবং কাযী আবুত তাইয়্যেব, দারিমী ও আবু আলী ছিনজী প্রমুখ একে সহীহ বলেছেন। (আলমাজমূ শরহুল মুহাযযাব ৭/৪২৭, দারুল হাদীস, কাহেরা)
ইমাম নববী রাহ. এখানে শুধু الأكثر নয়; বরং বহুবচন الأكثرون ব্যবহার করেছেন। এ থেকে অনুমান করা যায়, কী বিপুলসংখ্যক শাফেয়ী ফকীহ ঐ সিদ্ধান্তকে সঠিক বলেছেন। ‘আলমাজমূ’-এর পূর্ণ আলোচনা, যা এখানে নকল করা হয়নি এবং ফিকহে শাফেয়ীর অন্যান্য কিতাব থেকে এ আলোচনা আদ্যোপান্ত পড়া হলে দেখা যাবে, শাফেয়ী মাযহাবের উভয় ঘরানা ‘ইরাকী তরীকা’ ও ‘খুরাসানী তরীকা’র অধিকাংশ ফকীহ এ মতই গ্রহণ করেছেন। আর উভয় ঘরানার শায়খ (প্রধান) আবু হামিদ আসফারাইনী রাহ ও কাফফাল মারওয়াযী রাহ.-এর অবস্থানও তাই।
‘আলমাজমূ’ তো ইমাম আবু ইসহাক শীরাজী (৩৯৩ হি.-৪৭৬ হি.) কৃত ‘আলমুহাযযাব’-এর ভাষ্যগ্রন্থ, ‘আলমুহাযযাব’-এর মতো ফিকহে শাফেয়ীর দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কিতাব ইমাম গাযালী রাহ.-এর ‘আলওজীয’। এর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ভাষ্যগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয় ইমাম আবদুল কারীম রাফেয়ী (৬২৩ হি.)-এর ‘ফাতহুল আযীয’, যা ‘আশশরহুল কাবীর’ নামে প্রসিদ্ধ।
শাফেয়ী মাযহাবে রাফেয়ী ও নববীকে ‘শায়খাইন’ উপাধিতে স্মরণ করা হয় এবং এঁদের সম্মিলিত মতামত (متفقه تصحيح وترجيح) কে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে পাঠক নববী রাহ.-এর আলোচনা পাঠ করেছেন। এবার রাফেয়ীর বক্তব্য দেখুন-
إذا رئي الهلال في بلدة ولم ير في أخرى نظر، إن تقاربت البلدتان فحمهما حكم البلدة الواحدة، وإن تباعدتا فوجهان : أظهرهما، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله، وهو اختيار الشيخ أبي حامد أنه لا يجب الصوم على أهل البلدة الأخرى ...
والثاني : يجب، وهو اختيار القاضي أبي الطيب، ويروى عن أحمد ...
এক শহরে চাঁদ দেখা গেল, অন্য শহরে দেখা গেল না এ অবস্থায় দেখতে হবে : যদি শহর দুটি কাছাকাছি হয়, তাহলে দুটোকে এক শহরের মতো গণ্য করা হবে। (অর্থাৎ এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গার জন্যও অবশ্যঅনুসরণীয় হবে) আর যদি শহর দুটি পরস্পর দূরবর্তী হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে দুটি ‘ওয়াজহ’ রয়েছে : অধিক জাহির (অর্থাৎ দলিলের বিচারে অধিক স্পষ্ট এবং গ্রহণকারীর সংখ্যার বিচারে অধিক প্রসিদ্ধ) ‘ওয়াজহ’ এই যে, দ্বিতীয় শহরের অধিবাসীদের রোযা রাখা জরুরি হবে না। আবু হানীফা রাহ. এ-ই বলেছেন এবং শায়খ আবু হামিদও তা গ্রহণ করেছেন।
‘দ্বিতীয় ওয়াজহ’ এই যে, রোযা রাখা জরুরি হবে। কাযী আবুত তাইয়েব তা গ্রহণ করেছেন আর আহমদ রাহ. থেকেও তা বর্ণিত।’’
(ফাতহুল আযীয শরহুল ওয়াজীয, আবদুল করীম রাফেয়ী, কিতাবুস সওম ৩/১৭৯-১৮০)
রাফেয়ী রাহ.-এর বৃত্তান্ত থেকে এ-ও বোঝা গেল, কাছাকাছি শহর-নগরের ক্ষেত্রে সব ইমাম একমত যে, এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গার জন্য অবশ্যঅনুসরণীয়। মতভেদ দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে।
তেমনি এ-ও জানা গেল যে, মতভেদের ক্ষেত্রে শাফেয়ী মাযহাবের ‘আযহার’ তথা বেশি যাহির ও অগ্রগণ্য মত, যা তা ইমাম রাফেয়ীর দৃষ্টিতে ইমাম আবু হানীফারও মত। তবে আমার জানা নেই, আবু হানীফার এ মত তিনি কোথায় পেয়েছেন। না কি তার উদ্দেশ্য এ কথা বলা যে, হানাফী মাযহাবেরও অগ্রগণ্য মত এটি। অর্থাৎ ‘আবু হানীফা’ বলে তিনি ‘হানাফী মাযহাব’ নির্দেশ করেছেন।
ফিকহে শাফেয়ীর বহু গ্রন্থ মাশাআল্লাহ মুদ্রিত। সেসব থেকে নকল করতে থাকলে লেখা অনেক দীর্ঘ হয়ে পড়বে। তাই এখানে ফিকহে শাফেয়ীর কিছু কিতাবের শুধু বরাত উল্লেখ করছি। আগ্রহী পাঠক সেগুলো খুলে দেখতে পারেন।
1. ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, ইমাম গাযালী শাফেয়ী (৪৫০-৫০৫ হি.)
ইমাম গাযালী রাহ.-এর এই কিতাব তো মাশাআল্লাহ আম-খাস, আলিম-বুদ্ধিজীবী সব মহলে সমান সমাদৃত। এতে (১/৩৩৮) সিয়ামের আলোচনায় প্রথম পরিচ্ছেদেই এ মাসআলা আছে। তিনি পরিষ্কার লিখেছেন-
إذا رؤي ببلدة ولم ير بأخرى وكان بينهما أقل من مرحلتين وجب الصوم على الكل، وإن كان أكثر كان لكل بلدة حكمها ولا يتعدى الوجوب.
2. আততাহযীব ফী ফিকহিল ইমামিশ শাফেয়ী, আবু মুহাম্মাদ হুসাইন ইবনে মাসউদ আলবাগাভী (৫১৬ হি.) (৩/১৪৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত, প্রথম প্রকাশ : ১৪১৮ হি., ১৯৯৭ ঈ.)
3. আলবায়ান ফী মাযহাবিল ইমামিশ শাফেয়ী (৩/৪৭৮, দারুল মিনহাজ, জিদ্দা), আবুল হুসাইন ইয়াহইয়া ইবনে আবিল খায়ের আলইমরানী আশশাফেয়ী (৪৮৯-৫৫৮)
4. রওযাতুত তালেবীন ওয়া উমদাতুল মুফতীন (২/৩৪৮), ইমাম নববী শাফেয়ী (৬৩১-৬৭৬ হি.)
5. তুহফাতুল মুহতাজ শরহুল মিনহাজ (৪/৫০৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত), ইবনে হাজার মক্কী হাইতামী শাফেয়ী (৯৭৪ হি.)
6. মুগনিল মুহতাজ শরহুল মিনহাজ (১/৫৬৯, দারুল ফিকর, বৈরুত), আলখতীবুশ শিরবীনী শাফেয়ী (৯৭৭ হি.)
7. নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ (৩/২৩৫-২৩৬, আলমাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যা, কায়রো), শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ আররামলী শাফেয়ী (১০০৪ হি.)
মিনহাজ ফিকহে শাফেয়ীর নির্ভরযোগ্যতম ‘মতন’। এর অনেক ভাষ্যগ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে ‘তুহফাতুল মুহতাজ’ ও ‘নিহায়াতুল মুহতাজ’ শাফেয়ী ফকীহগণের কাছে সবচেয়ে বেশি সমাদৃত। মিনহাজের অন্য অনেক শরহের মতো এ দুটোতেও আলোচিত মাসআলায় শায়খাইন (রাফেয়ী ও নববী)-এরই সহমত পোষণ করা হয়েছে।
8. আলফাতাওয়াল ফিকহিয়্যাহ, ইবনে হাজার মক্কী হাইতামী ২/৬০
9. আহকামুল কুরআন (১/৭০) ইলকিয়া আততবারী (৪৫০-৫০৪ হি.)
10. বাহরুল মাযহাব, আবুল মাহাসিন আররুয়ানী (৪১৫-৫০২ হি.)
শেষোক্ত দুই কিতাবের আলোচনা এখানে তুলে দেওয়া মুনাসিব মনে হচ্ছে। ইমাম ইলকিয়া তবারী (শামসুল ইসলাম আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইলকিয়া আলহাররাছী) ‘‘আহকামুল কুরআনে’’ লেখেন-
وأجمع أصحاب أبي حنيفة على أنه إذا صام أهل بلد ثلاثين يوما للرؤية، وأهل بلد تسعة وعشرين يوما، أن على الذين صاموا تسعة وعشرين قضاء يوم.
وأصحاب الشافعي لا يرون ذلك، إذ كانت المطالع في البلدان يجوز أن تختلف.
অর্থ, আসহাবে আবু হানীফার (অর্থাৎ হানাফী মাযহাবের ধারক-বাহক ফকীহবৃন্দের) ইজমা আছে যে, যদি কোনো শহরের অধিবাসীরা চাঁদ দেখে ত্রিশ রোযা রাখে তাহলে যে শহরের অধিবাসীরা উনত্রিশ রোযা রেখেছে তাদেরকে একদিনের রোযা কাযা করতে হবে।
আর আসহাবে শাফেয়ী (অর্থাৎ শাফেয়ী মাযহাবের ধারক-বাহক ফকীহবৃন্দ) একে জরুরি মনে করেন না। কারণ দুই শহরের উদয়স্থলে পার্থক্য হতে পারে। (আহকামুল কুরআন, ইলকিয়া তবারী ১/৭০; আলজামি লিআহকামিল কুরআন, কুরতুবী ৩/১৫৭, আলবাকারা ২ : ১৮৫)
ইলকিয়া রাহ. আপন মাযহাব সম্পর্কে যা বলেছেন সে সম্পর্কে আমার কোনো মন্তব্য নেই। তিনিই তাঁর মাযহাব সম্পর্কে ভালো জানেন। কিন্তু আসহাবে আবু হানীফার বিষয়ে তিনি যা লিখেছেন সে সম্পর্কে মনে রাখতে হবে, এ মাসআলা শুধু আবু ইউসুফ রাহ. ও মুহাম্মাদ রাহ. থেকে বর্ণিত এবং অধিকাংশ বড় বড় হানাফী ফকীহ এ বিধানকে শুধু কাছাকাছি শহর-নগরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করেন, যা ইতিপূর্বে নির্ভরযোগ্য বরাত সহকারে লেখা হয়েছে। আমার ধারণা, এখানে ইলকিয়া রাহ.-এর বিভ্রান্তি হয়েছে আবু বকর রাযী রাহ.-এর বক্তব্য থেকে। এ কারণে তিনি ব্যতিক্রমহীনভাবে ‘আসহাবে আবু হানীফা’র সাথে একটি কথা সম্বন্ধ করে বলে দিয়েছেন যে, ঐ বিষয়ে সকলের ইজমা আছে।
মূল ঘটনা এই যে, জাসসাস রাহ. ‘‘আহকামুল কুরআনে’’ আল্লাহ তাআলার বাণী- فعدة من ايام اخر এর অধীনে দুটি মাসআলা উল্লেখ করেছেন : এক. যে ব্যক্তি অসুস্থতার কারণে রমযানে কোনো রোযা রাখতে পারেনি সে কয়দিনের রোযা কাযা করবে-উনত্রিশ না ত্রিশ।
দুই. কোনো শহরে ত্রিশ দিন রোযা রাখা হয়েছে তাহলে যারা উনত্রিশ রোযা রেখেছে তাদেরকে একদিনের রোযা কাযা করতে হবে কি না।
এই দুই মাসআলার বর্ণনা জাসসাস রাহ. এভাবে শুরু করেছেন-
ذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف، وهشام عن محمد، من غير خلاف من أحد من أصحابنا، قالوا ... .
অর্থাৎ, বিশর ইবনুল ওয়ালীদ আবু ইউসুফ রাহ. থেকে, এবং হিশাম মুহাম্মাদ রাহ. থেকে বর্ণনা করেন-আর এ বিষয়ে আমাদের ইমামদের থেকে বিপরীত কোনো সিদ্ধান্ত বর্ণিত হয়নি-তাঁরা বলেন, ...।
এভাবে কথা শুরু করে জাসসাস মাসআলা দুটি বলেছেন যে, অসুস্থ ব্যক্তি যে শহরের অধিবাসী ঐ শহরের অধিবাসীরা যদি ২৯ রোযা রেখে থাকে তাহলে তাকেও উনত্রিশ রোযা কাযা করতে হবে। আর কোনো শহরে যদি চাঁদ দেখার ভিত্তিতে ত্রিশ রোযা রাখা হয় এবং উনত্রিশওয়ালারা তা জানতে পারেন তাহলে তাদের একদিনের রোযা কাযা করা জরুরি। (আহকামুল কুরআন, জাসসাস ১/২২০)
জাসসাসের বক্তব্যের অর্থ, এ মাসআলা আবু ইউসুফ রাহ. ও মুহাম্মাদ রাহ. থেকে (নাদির রেওয়ায়েতে বিশর ও হিশামের সূত্রে) বর্ণিত হয়েছে। আর আমাদের অন্য কোনো ইমাম থেকে এ মাসআলা বর্ণিত না হলেও বিপরীত সিদ্ধান্ত তাদের থেকে বর্ণিত হয়নি। এ হচ্ছে তাঁর বক্তব্য। কিন্তু চিন্তা না করলে এ বক্তব্য পড়ামাত্র কারো মনে হতে পারে এর অর্থ, ‘‘আমাদের সকল ফকীহ এমনটা বলেছেন, কেউ এ বিষয়ে দ্বিমত করেননি।’’ সম্ভবত ইলকিয়া রাহ.-এর এ বিভ্রান্তিই হয়েছে এবং এরই ভিত্তিতে তিনি এ কথাটিকে সকল হানাফী ফকীহর ইজমাকৃত মাসআলা বানিয়ে দিয়েছেন!!
অথচ জাসসাস রাহ.-এর উদ্দেশ্য কখনো এই নয় যে, এটি ফিকহে হানাফীর ইজমায়ী মাসআলা। এখানে ইলকিয়া রাহ.-এর এক ‘তাসামুহ’ তো এই যে, ইজমায়ী নয় এমন মাসআলাকে ইজমায়ী বানিয়ে দিয়েছেন। আর দ্বিতীয় তাসামুহ এই যে, এ মাসআলা কি সকলস্থানের জন্য প্রযোজ্য, না শুধু কাছাকাছি শহর-নগরের ক্ষেত্রে-এ দিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ করেননি। অথচ বড় বড় অনেক হানাফী ফকীহ একে শুধু কাছাকাছি শহর-নগরের বিধান মনে করেন।
যাহোক, বিষয়টি প্রসঙ্গক্রমে এসেছিল। আলোচনা হচ্ছিল শাফেয়ী মাযহাব সম্পর্কে, তো এ বিষয়ে ফিকহে শাফেয়ীর অন্যান্য উদ্ধৃতির মতো ইলকিয়া রাহ.-এর উপরোক্ত উদ্ধৃতিরও মূলকথা হচ্ছে, শাফেয়ী মাযহাবে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য।
এবার শুনুন আবুল মাহাসিন রুয়ানী রাহ.-এর ‘বাহরুল মাযহাব’-এর বরাত। ফিকহে শাফেয়ীতে আবুল মাহাসিন রুয়ানীর মাকাম ও অবস্থান কী তা এ ঘটনা থেকেও অনুমান করা যায় যে, একবার তিনি আল্লাহর নেয়ামতের বর্ণনা হিসেবে বলেছেন-
لو احترقت كتب الشافعي لأ مليتها من حفظي
অর্থাৎ আল্লাহ না করুন, যদি শাফেয়ীর গ্রন্থাবলী পুড়ে ছাই হয়ে যায় তাহলে আমি তা নিজ স্মৃতি থেকে লিখিয়ে দিতে পারব। (তবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাহ, তাজুদ্দীন সুবকী ৭/১৯৪)
তাঁর জন্ম ৪১৫ হিজরীতে। আর মৃত্যু ৫০২ হিজরীতে। আশুরার দিন জুমার আগে যখন তিনি ইমলার মজলিস থেকে ফারিগ হন ঐ সময় বাতেনী মালাউনেরা তাকে শহীদ করে দেয়। (রাহিমাহুল্লাহ ওয়া রাযিয়া আনহু)
তিনি ফিকহে শাফেয়ীর উপর অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। জীবনের শেষের দিকে লিখেছেন ‘বাহরুল মাযহাব গ্রন্থটি। এর ভূমিকায় তিনি লেখেন, ‘মাযহাব’ ও ‘খিলাফিয়্যাত’ বিষয়ে ছোট-বড় অনেক গ্রন্থ রচনা করেছি। পরে ইমামগণের আরো অনেক ফাওয়াইদ (মাসাইল ও দালাইল) সংগৃহীত হয়েছে। তো ইচ্ছে হল, জীবনের শেষদিকে এক কিতাবে আমার কথাগুলো একত্র করে দেই -
(أحببت أن أجمع كلامي في آخر عمري في كتاب واحد)
যাতে আমার জন্য জানা সহজ হয় যে, ঐ কিতাবগুলোতে কী আছে। আর এ গ্রন্থে আমি ‘আসাহ’ (أصح)-এর উপর নির্ভর করব। (অর্থাৎ অধিকতর বিশুদ্ধ ‘কওল’ ও ‘ওয়াজহে’র উপর এ কিতাবের বুনিয়াদ হবে) আর এর নাম রাখছি ‘বাহরুল মাযহাব।’ (বাহরুল মাযহাব, রুয়ানী, ভূমিকা)
তাঁর এ প্রিয়তম গ্রন্থে তিনি লেখেন, (অর্থ) এক শহরের অধিবাসীগণ চাঁদ দেখল অন্য শহরের অধিবাসীরা দেখল না-যদি দুই শহরের মাঝে দূরত্ব এত কম হয় যে, উদয়স্থল আলাদা হয় না, যেমন বাগদাদ ও বসরা, তাহলে অন্য শহরের অধিবাসীদের উপরও ঐ শহরের চাঁদ দেখার কারণে রোযা ফরয হবে।
আর যদি দুই শহর দূর-দূরান্তের হয় যেমন ইরাক ও হিজায বা শাম ও খোরাসান, তাহলে আবু হামেদ (আসফারাইনী, ইরাকী তরীকার শায়খ) বলেন, এক্ষেত্রে এক শহরের অধিবাসীদের অন্য শহরের অধিবাসীদের চাঁদ দেখা অনুসারে আমল করা জরুরি নয়। কাযী আবু হামেদ (আলমারওয়াররূযী, মৃত্যু : ৩৬২ হি.)ও এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ...।
এরপর রুয়ানী এর দলীল উল্লেখ করেছেন। অতপর কাযী আবুত তাইয়েব তবারীর সিদ্ধান্ত উল্লেখ করেছেন যে, এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য সর্বাবস্থায় অবশ্যঅনুসরণীয়। এরপর রুয়ানী লেখেন- والأول أظهر عندي অর্থাৎ প্রথম সিদ্ধান্তই আমার কাছে অধিক ‘জাহির’ (স্পষ্ট ও প্রসিদ্ধ)। (বাহরুল মাযহাব, আবুল মাহাসিন রুয়ানী ৪/২৭১, দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, বৈরুত)
আবুল মাহাসিন রুয়ানীর শেষজীবনের এ কিতাবের বর্ণনার আলোকে ‘তরহুত তাছরীব’ অলিউদ্দীন ইরাকীর* মুদ্রিত নুসখায় (৪/১১২) রুয়ানীর বরাতে যে বিবরণ আছে তা সংশোধন করে নেওয়া উচিত।
[টীকা : * আহকামের হাদীসের উপর যায়নুদ্দীন ইরাকীর অতি উত্তম কিতাব ‘তাকরীবুল আসানীদ ওয়া তারতীবুল মাসানীদ’। এরই শরহ-ভাষ্যগ্রন্থ হচ্ছে ‘তরহুত তাছরীব’। এর রচনা তিনি নিজেই শুরু করেছিলেন কিন্তু সমাপ্ত করেছেন তাঁর পুত্র অলিউদ্দীন ইরাকী। কিতাবুস সিয়ামের এ পরিচ্ছেদগুলো অলিউদ্দীন ইরাকীকৃত তাকমিলারই অংশ।]
তাতে এ স্পষ্ট বৃত্তান্তের পর যে, শাফেয়ী মাযহাবের কতিপয় মনীষী উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য মনে করেন না এবং এ বৃত্তান্তেরও পর যে, শায়খ আবু হামেদ (আসফারাইনী), আবু ইসহাক শীরাজী, গাযালী, শাশী (আবু বকর ফখরুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ৪২৯ হি-৫০৭ হি., হিলয়াতুল উলামার লেখক) ও অধিকাংশের নিকট ‘আসাহ’ অধিকতর সহীহ এই যে, দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক জায়গার চাঁদ দেখার কারণে অন্য জায়গায় রোযা জরুরি হবে না-এই দুই স্পষ্ট বিবরণের পর তরহুত তাছরীবের মুদ্রিত নুসখায় লেখা আছে-
والثاني : الوجوب، وإليه ذهب القاضي أبو الطيب، والروياني، وقال : إنه ظاهر المذهب، واختاره جميع أصحابنا.
অর্থাৎ দ্বিতীয় ‘ওয়াজহ’ এই যে, (দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক জায়গার চাঁদ দেখার কারণে অন্য জায়গায়) রোযা ওয়াজিব হবে। কাযী আবুত তাইয়েব এদিকেই গিয়েছেন, রুয়ানীও। তিনি বলেছেন, এটি ‘জাহিরুল মাযহাব।’ এবং একে আমাদের সকল আসহাব (সকল শাফেয়ী ফকীহ) গ্রহণ করেছেন।-তরহুত তাছরীব ৪/১১২, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ১৪২১ হিজরী)
আহমদ গুমারী এ বরাতের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে চিন্তা না করে এবং আগে-পরের স্পষ্ট কথাগুলোর দিকে লক্ষ্য না করে তার কিতাব ‘‘তাওজীহুল আনযার’’-এ তা নকল করে দিয়েছেন!!
চিন্তা করার বিষয় এই যে, যখন অধিকাংশ শাফেয়ী ফকীহ প্রথম
সিদ্ধান্তকে ‘আসাহ’ (অধিক বিশুদ্ধ/অগ্রগণ্য) বলছেন তখন দ্বিতীয় ওয়াজহের বিষয়ে واختاره جميع أصحابنا (আমাদের সকল ফকীহ তা গ্রহণ করেছেন) বলার কী অর্থ? এবং যখন ফিকহে শাফেয়ীর কিতাবসমূহে এ মাসআলায় শুধু শাফেয়ী ফকীহগণের মাসলাকই উল্লেখ করা হচ্ছে, সরাসরি ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর কোনো উক্তি/বক্তব্য কেউ উল্লেখই করছেন না, স্বয়ং রুয়ানীও উল্লেখ করেননি তাহলে একে ‘জাহিরুল মাযহাব’ বলা যায় কীভাবে?
পাঠক ইতিমধ্যে তার শেষ জীবনের কিতাব ‘বাহরুল মাযহাবের’ আলোচনা পাঠ করেছেন। ওখানে তিনি পরিষ্কার বলছেন-
والأول أظهر عندي
অর্থাৎ দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় না হওয়ার সিদ্ধান্তই আমার কাছে অধিক ‘জাহির’ (স্পষ্ট ও প্রসিদ্ধ)।
রুয়ানীর রচনাবলির মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত কিতাব ‘হিলয়াতুল মুমিন’। জামেয়া উম্মুল কুরার একজন তালিবে ইলম এর এক অংশের তাহকীক (পান্ডুলিপি-সম্পাদনা) করেছেন। তাঁর সামনে এ কিতাবের দুটো হস্তলিখিত পান্ডুলিপি ছিল। দুটোতেই অনেক জায়াগায় কিছু কিছু বাক্য অস্পষ্ট।
‘হিলয়াতুল মুমিন’ সম্পর্কে ইবনুস সালাহ রাহ. (৬৪৩ হি.) বলেছেন, এ কিতাবে তিনি শাফেয়ী মাযহাবের বাইরের অনেক সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেছেন (তাহযীবুল আসমা, নববী ১/৭৮৩)। এবং কাযী আবু শুহবা (৭৭৯-৮৫১ হি.) ‘তবাকাতুশ শাফেয়িয়্যাহ’য় বলেছেন, এতে মাযহাবের বাইরে তাঁর নিজের অনেক ‘‘ইখতিয়ারাত’’ বা ব্যক্তিগত মত আছে, যার অনেক কিছুই মালেক রাহ.-এর মাযহাবের মুয়াফিক। (শাযারাতুয যাহাব, ইবনুল ইমাদ ৪/৪, ৫০২ হি.)
হিলয়াতুল মুমিনের যে অংশ ঐ তালিবে ইলম তাহকীক করেছেন তাতে লেখা আছে-
ولو أن أهل بلد رأوا الهلال يلزم على جميع أهل البلاد الصوم في ذلك اليوم في ظاهر المذهب وهو اختيار جماعة من أصحابنا، وبه قال أحمد، ... وهو اختيار القاضي الطبري.
অর্থ, যদি কোনো শহরবাসী চাঁদ দেখে তাহলে অন্য সকল শহরের অধিবাসীদের উপর ঐ দিন রোযা রাখা জরুরি হবে, জাহের মাযহাব অনুযায়ী।
এটিই আমাদের আসহাবের (ফকীহদের) এক জামাতের গৃহীত সিদ্ধান্ত। আর আহমদ রাহ. এমনটি বলেছেন ... এবং কাযী তবারীর গৃহীত মাসলাকও তা। (হিলয়াতুল মুমিন, আবুল মাহাসিন রুয়ানী, তাহকীক, তালিবে ইলম মুহাম্মাদ ইবনে মাতার ইবনে আলী আলমালেকী, জামেয়া উম্মুল কুরা ১৪২৮ হি.)
‘‘হিলয়াতুল মুমিনে’র এ উদ্ধৃতি ‘তরহুত তাছরীবে’র সূত্র হতে পারে। তবে اختيار جماعة من أصحابنا (আমাদের ফকীহগণের মধ্যে এক জামাতের গৃহীত মাসলাক) বিকৃত হয়ে اختاره جميع أصحابنا (আমাদের সকল আসহাব তথা ফকীহগণের গৃহীত মাসলাক)-এ পরিণত হয়েছে।
এখন থাকল একে ‘জাহিরুল মাযহাব’ বলা, যদি ‘জাহিরুল মাযহাব’ শব্দবন্ধের বিষয়ে রুয়ানীর বা শাফেয়ী লেখকগণের নিজস্ব কোনো পরিভাষা* না থাকে তাহলে প্রবল সম্ভাবনা এই যে, ওখানে বাক্যের কিছু অংশ বাদ পড়ে গেছে। প্রাচীন ও স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখিত পান্ডুলিপি খুঁজলে প্রকৃত বিষয়টি বোঝা যাবে। আমার ধারণা, এখানে বাক্যটি এরকম হয়ে থাকবে-
في ظاهر مذهب مالك، وهو اختيار جماعة من أصحابنا
অর্থাৎ (উপরোক্ত সিদ্ধান্ত) মালেক রাহ.-এর মাযহাবের জাহির অনুযায়ী। আর তা আমাদের এক জামাত আসহাবের (ফকীহের) গৃহীত মাসলাক।
ফিকহের কিতাবের সাথে অন্তরঙ্গতা রাখা তালিবে ইলমগণ চিন্তা করলে দেখবেন في ظاهر المذهب (ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর মাযহাবের জাহের রেওয়ায়েত) বলার পর (وهو اختيار جماعة من أصحابنا) বাক্যটি অসংলগ্ন মনে হয়। এ বাক্য তখনই সংলগ্ন হতে পারে যখন ইতিপূর্বে অন্য কোনো ইমাম বা ফকীহের মাযহাব বর্ণনা করা হবে। অন্যথায় যে মাসলাক ইমাম শাফেয়ীর জাহির রেওয়ায়েত তা তো ঐ মাযহাবের একদল ফকীহর নয়, অধিকাংশ ফকীহর মাসলাক হবে। আর তা হবে ‘ইত্তিবা’র (অনুসরণের) ভিত্তিতে, ‘ইখতিয়ারে’র (পছন্দ ও গ্রহণের) ভিত্তিতে নয়। এটাই সাধারণ নিয়মের কথা।
যাহোক, এ বিষয়ে চূড়ান্ত ও নিশ্চিত কথা তো ‘হিলয়াতুল মুমিনে’র প্রাচীন পান্ডুলিপিসমূহ এবং এর লেখকের পরিভাষাসমূহের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের পর এবং এ যুগের গবেষক শাফেয়ী আলিমগণের শরণাপন্ন হওয়ার পরই বলা যেতে পারে। আফসোস, এ মুহূর্তে আমার পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ তাআলা হয়তো এর সুযোগ করে দিবেন। আমীন।
কিন্তু যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, ‘হিলয়াতুল মুমিনে’ রুয়ানীর এ বাক্য এভাবেই আছে এবং এর সাধারণ অর্থই উদ্দেশ্য তাহলে বলাই বাহুল্য যে, এটি একটি অবাস্তব কথা, যা তাঁর শেষ জীবনে লেখা ‘‘বাহরুল মাযহাবে’’র বিবরণেরও পরিপন্থী। এতে তিনি দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় না হওয়াকেই ‘আযহার’ বলেছেন। আর তাঁর আগের-পরের অধিকাংশ শাফেয়ী ফকীহর বক্তব্যও তা-ই। وبالله التوفيق
* টীকা :
যেমন এ পরিভাষা হতে পারে যে, মাযহাবের কোনো ফকীহর (আসহাবুত তারজীহ স্তরের) দৃষ্টিতে যে সিদ্ধান্ত বিশুদ্ধ বা অগ্রগণ্য মনে হবে তিনি তাকে المذهب বা ظاهر المذهب শব্দে ব্যক্ত করেন। যদিও তা ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর কোনো ‘মানসূস আলাইহি’ স্পষ্ট বক্তব্য না হয়; বরং তাঁর মাযহাবের কোনো ফকীহর ইস্তিমবাত হয়।
কিংবা এ পরিভাষাও হতে পারে যে, মাযহাবের কোনো ফকীহ (মুজতাহিদ ফিল মাসাইল স্তরের, বা শাফেয়ীগণের পরিভাষা অনুযায়ী ‘আসহাবুল উজূহ’ স্তরের) যে সিদ্ধান্ত ইমাম শাফেয়ী রাহ. থেকে বর্ণিত কোনো মাসআলার ভিত্তিতে ইসতিখরাজ করেছেন এবং তা তাঁর দৃষ্টিতে শাফেয়ী মাযহাবের সিদ্ধান্ত হওয়ার দাবি রাখে, একে তিনি ‘জাহিরুল মাযহাব’ বলবেন।
কোনো লেখকের গ্রন্থে এ ধরনের কোনো পরিভাষার অনুসরণ বিচিত্র নয়। তবে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া নিশ্চিতভাবে কিছু বলা গবেষণার নীতির পরিপন্থী এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে না-জায়েয।
মালেকী মাযহাব
ইবনুল কাসিম রাহ. ও ইবনে ওয়াহব রাহ. ইমাম মালেক রাহ. থেকে বর্ণনা করেন-
إن أهل البصرة إذا رأوا هلال رمضان، ثم بلغ ذلك إلى أهل الكوفة والمدينة واليمن أنه يلزمهم الصيام أو القضاء إن فات الأداء.
অর্থ, বসরার লোকেরা রমযানের চাঁদ দেখল, এরপর এর সংবাদ কুফা, মদীনা ও ইয়ামানবাসীদের নিকট পৌঁছল তাহলে তাদের রোযা রাখা জরুরি হবে। আর সময় অতিবাহিত হয়ে থাকলে কাযা করা জরুরি হবে।
এ বর্ণনা মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আবদুস ‘‘আলমাজমুআ’’য় উল্লেখ করেছেন। ইনি ইমাম সুহনূনের অন্যতম বড় শাগরিদ। আর সুহনূন রাহ. হলেন ইবনুল কাসিম ও ইবনে ওয়াহবের শাগরিদ। আর এঁরা দুজন ইমাম মালিক রাহ.-এর মিসরী শাগরিদ।
‘‘কিতাবুল মাজমূআ’’ থেকে এ রেওয়ায়েত মুফাসসির আবু আবদুল্লাহ কুরতুবী (৬৭১ হি.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থ ‘আলজামি লিআহকামিল কুরআনে (৩/১৫৯) নকল করেছেন। আরো দেখুন : আননাওয়াদির ওয়ায যিয়াদাত, আবদুল্লাহ ইবনে আবু যায়েদ আলকাইরাওয়ানী (৩৮৬ হি.) খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১১; আলমুনতাকা শরহুল মুয়াত্তা, আবুল ওয়ালীদ আলবাজী (৪৯৪ হি.) খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৩০।
উল্লেখ্য, বসরা থেকে কুফার দূরত্ব ৩৬৭ কি.মি.। আর মদীনার দূরত্ব ১০৫০ কি.মি., ইয়ামানের দূরত্ব ১৭১৭ কি.মি. (আনুমানিক)।
এতো ছিল ইমাম মালেক রাহ.-এর মিসরী শাগরিদদ্বয়ের বর্ণনা। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক রাহ.-এর মাদানী শাগরিদ আবদুল মালিক ইবনুল মাজিশূন (২১২ হি.)-এর বর্ণনা কিছুটা আলাদা। তিনি বলেছেন-
إن كان ثبت بالبصرة بأمر شائع ذائع يستغني عن الشهادة والتعديل له، فإنه يلزم غيرهم من أهل البلاد القضاء، وإن كان إنما ثبت عند حاكمهم بشهادة شاهدين، لم يلزم ذلك من البلاد إلا من كان يلزمه حكمُ ذلك الحاكم ممن هو في وِلايته، أو يكون ثبت ذلك عند أمير المؤمنين، فيلزم القضاءُ جماعةَ المسلمين. قال : وهذا قول مالك.
বসরায় চাঁদ দেখা যদি এমন ব্যাপকভাবে প্রমাণিত হয়ে থাকে যে, সাক্ষ্য ও সাক্ষীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনই হয়নি তাহলে অন্য শহরের অধিবাসীদের ছুটে যাওয়া রোযার কাযা করতে হবে (অথবা অর্থ, অন্য শহরের অধিবাসীদের জন্য বসরার কাযীর ফয়সালাই অবশ্যঅনুসরণীয় হবে) আর যদি বসরার শাসকের কাছে দুই সাক্ষীর সাক্ষ্যের দ্বারা চাঁদ প্রমাণিত হয় তাহলে তা শুধু ঐ কাযীর কর্তৃত্বের এলাকায় অবশ্যঅনুসরণীয় হবে, অন্য শহরে নয়। তবে হ্যাঁ, আমীরুল মুমিনীনের কাছে চাঁদ প্রমাণিত হলে তাঁর ফয়সালা সকল মুসলিমের জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় হবে।
তিনি (ইবনুল মাজিশূন রাহ.) বলেন, এটা মালিক রাহ.-এর সিদ্ধান্ত। ইবনুল মাজিশূন রাহ.-এর এ বর্ণনা ইমাম আবু ইসহাক ইসমাইল ইবনে ইসহাক আলবাগদাদী আলমালেকী রাহ. (২০০-২৮২ হি.)-এর বরাতে মুফাসসির কুরতুবী ‘‘আলজামি লিআহকামিল কুরআনে’’ (৩/১৫৯) এবং ইমাম আবুল ওয়ালীদ বাজী রাহ. ‘‘আলমুনতাকা’’য় (২/৪৩০-৪৩১) নকল করেছেন।
এবং একে আরো স্পষ্ট ভাষায় ইমাম ইবনে আবী যায়েদ আলকাইরাওয়ানী (৩৮৬ হি.) ‘‘আননাওয়াদির ওয়ায যিয়াদাত’’ গ্রন্থে (২/১১) ইবনে হাবীব (আবদুল মালিক ইবনে হাবীব, ‘আলওয়াজিহা’ লেখক ও ইবনুল মাজিশূন এর শাগরিদ)-এর বরাতে নকল করেছেন। ওখানে শেষ বাক্যটি এই - (وهذا قول مالك وأصحابه)
অর্থাৎ এটি মালিক রাহ. ও তাঁর শাগরিদগণের সিদ্ধান্ত।
ইমাম মালেক রাহ.-এর ঐ শাগরিদদের মাঝে মুগীরা ইবনে আবদুর রহমান (১২৪-১৮৮ হি.) ও মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে দীনার (১৮২ হি.) বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত। ইবনে আবদুল বার রাহ. ‘‘আলইসতিযকারে’’ (১০/২৯) ইবনুল মাজিশূনের সাথে তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন।
(وهو قول المغيرة وابن دينار وابن الماجشون)
পরবর্তীতে মালেকী মাযহাবের কিতাবসমূহে সাধারণভাবে ইবনুল কাসিমের বর্ণনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং এটিই তাঁদের প্রসিদ্ধ মাযহাব। কিন্তু চিন্তা করার বিষয় এই যে, ইবনুল কাসিম ও ইবনুল মাজিশূন উভয়ের বর্ণনায় মাসআলার প্রেক্ষাপট এই ধরা হয়েছে যে, বসরায় চাঁদের সিদ্ধান্ত হয়েছে আর এর সংবাদ কুফা, মদীনা ও ইয়েমেনে পৌঁছেছে।
এ প্রেক্ষাপট বর্ণনায় তাঁর উদ্দেশ্য কি শুধু একটি উদাহরণ দেওয়া, না এ কথা জানানো যে, এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকায় অবশ্যঅনুসরণীয় তখনই হবে যখন এদের পরস্পরের দূরত্ব অনেক বেশি না হবে; বরং কাছাকাছি হবে বা দূরের হলেও খুব বেশি দূরের না হবে।
মালেকী মাযহাবের অনেক লেখক বিষয়টি পরিষ্কার না করলেও কোনো কোনো গবেষক ফকীহ একথা স্পষ্ট বলেছেন যে, ইমাম মালিক রাহ.-এর বক্তব্যে যে শহরগুলোর কথা এসেছে এ দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, পরস্পর দূরত্ব খুব বেশি হলে এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় হবে না।
যে লেখকগণ একে সর্বাবস্থার বিধান হিসেবে বর্ণনা করেছেন তাঁদের একজনের বরাত নকল করছি।
আবুয যিয়া খলীল ইবনে ইসহাক (৭৬৭ হি.)-এর ‘‘মুখতাসারু খলীল’’ ফিকহে মালেকীর এক প্রসিদ্ধ মতন। এর অনেক শরহ-হাওয়াশী (ভাষ্য ও টীকা) রচিত হয়েছে। এক শরহ আল্লামা আবুল বারাকাত আহমদ ইবনে আহমদ দরদের মালেকী (১১২৭-১২০১ হি.)-এর রচিত, যা ‘আশশারহুল কাবীর’ নামে প্রসিদ্ধ। এই শরহের উপর আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ দুসূকী (১২৩০ হি.)-এর হাশিয়া (টীকা) আছে এবং দুটো একসাথে মুদ্রিত।
দরদের লেখেন-
(وعَمَّ) الصومُ سائر البلاد قريبا أو بعيدا، ولا يراعى في ذلك مسافة قصر، ولا اتفاق المطالع ولا عدمها، فيجب الصوم على كل منقول إليه (إن نقل) ثبوته (بهما) أي بالعدلين أو المستفيضة (عنهما) أي عن العدلين، أو عن المستفيضة.
فالصور أربع : استفاضة عن مثلها، أو عن عدلين، وعدلان عن مثلهما، أو عن استفاضة.
ولا بد في شهادة النقل عن الشاهدين أن ينقل عن كل واحد اثنان، فيكفي نقل اثنين عن واحد، ثم عن الآخر، ولا يكفي نقل واحد عن واحد ... وأما النقل عن الحكم بثبوت الهلال برؤية العدلين، فإنه يعم ولو نقل الثبوت عند الحاكم واحد على الراجح.
দরদের রাহ.-এর এ বর্ণনার সারকথা এই যে, এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গার জন্যও অবশ্যঅনুসরণীয়। যদিও এ দুই জায়গার মাঝে কসরের দূরত্ব বা তার চেয়েও বেশি দূরত্ব হয় এবং যদিও দুই জায়গার উদয়স্থল আলাদা হয়। তবে শর্ত এই যে, শরীয়তমতে চাঁদ প্রমাণিত হতে হবে। এরপর তিনি চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন এবং এও বলেছেন যে, কোনো শহরের কাযীর চাঁদের ফয়সালা একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিও যদি অন্য শহরে পৌঁছে দেয় তাহলে তাঁর দৃষ্টিতে অগ্রগণ্য মত অনুসারে এ ফয়সালার উপর আমল করা জরুরি হবে। (আশশরহুল কাবীর ১/৫১০-৫১১, দারুল ফিকর, বৈরুত)
‘‘আশশরহুল কাবীর’’ এ মুহূর্তে আমার সামনে নেই। আমি এ উদ্ধৃতি উস্তাযে মুহতারাম হযরত শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ তকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম-এর প্রবন্ধ رؤية الهلال : قبول الشهادة برؤية الهلال وموانعها থেকে নকল করেছি। প্রবন্ধটি بحوث في قضايا فقهية معاصرة -এর দ্বিতীয় সংস্করণের, যা দারুল কলম দামেশক কর্তৃক ১৪৩২ হিজরী, ২০১১ ঈসায়ী প্রকাশিত, দ্বিতীয় খন্ডে আছে।
পরবর্তী (মুতাআখখিরীন) মালেকী ফকীহগণের বিপরীতে এ মাযহাবের একাধিক গবেষক ফকীহ, ইলমে হাদীস ও ইলমে তাফসীরে যাঁদের অনেক উঁচু মাকাম রয়েছে, স্পষ্ট বলেছেন, যে সকল অঞ্চল পরস্পর অনেক বেশি দূরবর্তী সেগুলোতে এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় নয়। যেমন -
1. ইমাম আবু উমার ইবনে আবদিল বার মালেকী রাহ. (৪৬৩ হি.) ‘‘আলইসতিযকার’’ গ্রন্থে ইমাম মালেক রাহ.-এর মিসরী শাগরিদ ও মাদানী শাগরিদগণের বর্ণনা ও অন্যান্য ফকীহগণের মাযহাব বর্ণনার পর লেখেন-
2. وأجمعوا أنه لا تُراعى الرؤية فيما أخر من البلدان كالاندلس من خراسان.
অর্থাৎ তাঁরা সবাই এ বিষয়ে একমত যে, যে সকল শহর পরস্পর অনেক বেশি দূরে অবস্থিত যেমন আন্দালুস থেকে খোরাসান, সেখানে এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গায় প্রযোজ্য হবে না। (আলইসতিযকার শরহুল মুয়াত্তা ১০/৩০)
ইবনে আবদুল বার রাহ. আন্দালুসের কুরতুবা (কর্ডোবা) নগরীর অধিবাসী ছিলেন। কুরতুবা থেকে (উত্তর) খোরাসান (আনুমানিক) ৫৩০৩) কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।
3. আবু বকর ইবনুল আরাবী
এমনিভাবে কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী মালেকী (মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ৪৬৮-৫৪৩ হি.) তাঁর কিতাব ‘‘আরিযাতুল আহওয়াযী’’ (৩/২১০-২১১)-এর আলোচনার বিপরীতে তার অন্য কিতাব ‘‘আহকামুল কুরআনে’’ লেখেন-
إذا أخبر مخبر عن رؤية بلد فلا يخلو أن يقرب أو يبعد، فإن قرب فالحكم واحد، وإن بعد فقد قال قوم : لأهل كل بلد رؤيتهم. وقيل يلزمهم ذلك ...
واختلف في تأويل قول ابن عباس هذا، فقيل : رده لأنه خبر واحد، وقيل : رده، لأن الأقطار مختلفة في المطالع، وهو الصحيح، لأن كريبا لم يشهد، وإنما أخبر عن حكم ثبت بشهادة، ولا خلاف في أن الحكم الثابت بالشهادة يجزئ فيه خبر الواحد.
ونظيره ما لو ثبت أنه أهل ليلة الجمعة بأَغْمَات، وأهل بإشبيلية ليلة السبت، فيكون لأهل كل بلد رؤيتهم ...
অর্থ, কেউ যদি অন্য কোনো শহরে চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সংবাদ দেয় তাহলে হয়তো সে শহর কাছে হবে অথবা দূরে। যদি কাছে হয় তাহলে দুই শহরের বিধান একই। আর দূরে হলে এক দল (ফকীহগণের এক জামাত) বলেন, প্রত্যেক শহরের অধিবাসীদের জন্য নিজেদের চাঁদ দেখাই ধর্তব্য। আবার এ কথাও বলা হয়েছে যে, তাদের জন্যও (সে চাঁদ দেখা) অবশ্যঅনুসরণীয়। (এরপর ইবনে আরাবী রাহ. আদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর ঐ হাদীস উল্লেখ করে বলেন) ইবনে আববাস রা.-এর এ বক্তব্যের ব্যাখ্যায় ইখতিলাফ আছে : কেউ বলেছেন, তিনি এর (শামে চাঁদ দেখার) ইতিবার এজন্য করেননি যে, বর্ণনাকারী ছিলেন একজন। আর কেউ বলেছেন, ইতিবার না করার কারণ দুই এলাকার উদয়স্থল আলাদা হওয়া। এটিই সঠিক কথা। কারণ কুরাইব তো ফয়সালার সংবাদ দিয়েছিলেন। আর এতে কোনো দ্বিমত নেই যে, কাযীর ফয়সালা নকল করার ক্ষেত্রে একজনের সংবাদও গ্রহণযোগ্য। (তাই ইতিবার না করার কারণ সংবাদদাতা একজন হওয়া নয়, উদয়স্থল আলাদা হওয়া।)
এর দৃষ্টান্ত এমন যে, যদি ‘আগমাত’-এ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে চাঁদ দেখা যায় আর ইশবীলিয়্যায় শুক্রবার দিবাগত রাতে, তাহলে এক্ষেত্রে প্রত্যেক শহরের অধিবাসীদের নিজেদের চাঁদ দেখাই ধর্তব্য হবে।-আহকামুল কুরআন, ইবনুল আরাবী ১/৮৪-৮৫
আর আগমাত থেকে ইশবিলিয়্যার দূরত্ব ৬৮১ কি.মি (আনুমানিক)
4. ইবনে রুশদ আলহাফীদ
ইমাম আবুল ওয়ালীদ ইবনে রুশদ (৫২০-৫৯৫ হি.)ও ‘‘বিদায়াতুল মুজতাহিদ’’ গ্রন্থে ইমাম মালিক রাহ.-এর মিসরী শাগরিদ ও মাদানী শাগরিদদের বর্ণনা উল্লেখ করার পর লেখেন-
وأجمعوا أنه لا يُراعى ذلك في البلدان النائية، كالأندلس والحجاز.
এবং সবাই এ বিষয়ে একমত যে, অনেক দূরের শহরসমূহে যেমন আন্দালুস ও হিজাযে এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলে ধর্তব্য হবে না। (বিদায়াতুল মুজতাহিদ ১/৩৫৮, দারুল আকীদা, কাহেরা)
(আন্দালুস থেকে মদীনা ৪৪৪৪ কি.মি. আনুমানিক)
5. আবুল আববাস কুরতুবী
ফিকহ ও হাদীসের ইমাম আল্লামা আবুল আববাস আহমদ ইবনে উমার আলকুরতুবী (৫৭৮-৬৫৬ হি.) সহীহ মুসলিমের সংক্ষেপণ করেছেন। এরপর ‘আলমুফহিম’’ নামে নিজেই এর শরহ (ভাষ্য) লিখেছেন। এতে ‘কিতাবুস সওম-এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম এই-
باب لأهل كل بلد رؤيتهم عند التباعد ...
অর্থাৎ, দূরে দূরে হলে প্রত্যেক শহরের জন্য নিজেদের চাঁদ দেখাই ধর্তব্য।
এ পরিচ্ছেদের ভাষ্যে তিনি লিখেছেন-অর্থ, আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর এ বাণী-
هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এরূপ আদেশ করেছেন) মারফূ হাদীস হওয়া স্পষ্ট। সুতরাং এ হাদীস দলিল যে, যেসব শহর শাম ও হিজাযের মতো দূরে দূরে অবস্থিত সেখানে প্রত্যেককে নিজ নিজ চাঁদ দেখা অনুসারে আমল করা চাই, যদিও কোনো জায়গার চাঁদ দেখা আমীরুল মুমিনীনের কাছেও প্রমাণিত হয়। হ্যাঁ, আমীরুল মুমিনীনের কাছে চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার পর তিনি যদি ব্যাপকভাবে এর ফয়সালা করেন এবং সবাইকে সে অনুসারে আমলের হুকুম করেন তাহলে প্রত্যেককে এই চাঁদ দেখার উপরই আমল করতে হবে। আমীরের বিরোধিতা করা বৈধ হবে না। কারণ এ মাসআলা ইজতিহাদী ও ইখতিলাফী। আর আমীরুল মুমিনীনের ফয়সালার পর বিপরীত ইজতিহাদের কার্যকারিতা থাকে না। সুতরাং তাঁর বিরোধিতা অবৈধ হবে। তাঁর ভাষায়-
... فالواجب على أهل كل بلد أن تعمل على رؤيته دون رؤية غيره، وإن ثبت ذلك عند الإمام الأعظم، ما لم يحمل الناس على ذلك فلا تجوز مخالفته، إذ المسألة اجتهادية مختلف فيها، ولا يبقى مع حكم الإمام اجتهاد، ولا تحل مخالفته.
আবুল আববাস কুরতুবী রাহ. তাঁর আলোচনায় সামনে গিয়ে বলেন-
وحكى أبو عمر ابن عبد البر الإجماع على أنه لا تُراعى الرؤية فيما بعد من البلدان كالأندلس من خراسان، قال : ولكل بلد رؤيتهم، إلا ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره من بلدان المسلمين.
قلت : وهذا الإجماع الذي حكاه أبو عمر يدل على أن الخلاف الواقع في هذه المسألة إنما هو فيما تقارب من البلاد، ولم يكن في حكم القطر الواحد.
এই উদ্ধৃতির সারকথা হচ্ছে, ইবনে আবদুল বার রাহ. এ বিষয়ে ইজমা নকল করেছেন যে, অনেক বেশি দূরের শহর-নগরে, যেমন আন্দালুস থেকে খোরাসান, এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গায় ধর্তব্য হবে না। এই ইজমা থেকে জানা গেল যে, উদয়স্থলের ভিন্নতা প্রসঙ্গে যে ইখতিলাফ তা এমন শহর-নগরের ক্ষেত্রে, যা একে অপর থেকে অনেক বেশি দূরে নয়, যে কারণে কুতরই (প্রান্ত) আলাদা হয়ে যায়।
এরপর মালেকী মাশায়েখের বক্তব্য যে, নিকট-দূর সকল ক্ষেত্রে এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গার জন্য ধর্তব্য এর উপর পর্যালোচনা করে আবুল আববাস কুরতুবী রাহ. বলেন, মাশায়েখদের এ কথাকে ইবনে আবদুল বার রাহ.-এর নকলকৃত ইজমার আলোকে বুঝতে হবে। তিনি লেখেন-
هكذا وقع نقل المشايخ لهذه المسألة، ولم يفرقوا بين البعيد والقريب من الأقاليم، والصواب الفرق، بدليل الإجماع الذي حكاه أبو عمر، فيحمل إطلاق المشايخ على البلاد المتقاربة، والله تعالى أعلم.
(আলমুফহিম লিমা আশকালা মিন তালখীছি কিতাবি মুসলিম ৩/১৪২-১৪৪, দারু ইবনে কাছীর, দিমাশক ও বৈরুত)
আবুল আববাস কুরতুবীর শাগরিদ মুফাসসির আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ কুরতুবী (৬৭১ হি.) ‘আলজামি লিআহকামিল কুরআন’’-এ নিজ শায়খের বিভিন্ন কথা বর্ণনা করেছেন। ইবনুল আরাবী ও ইবনে আবদিল বার এর বরাতও উল্লেখ করেছেন। আগ্রহী পাঠক তাঁর আলোচনা ‘আলজামি লিআহকামিল কুরআন (৩/১৫৭-১৫৯, সূরাতুল বাকারার আয়াত : ১৮৫-এর অধীনে) দেখতে পারেন।
তদ্রূপ ইমাম শিহাবুদ্দীন আবুল আববাস আলকারাফী আহমদ ইবনে ইদরীছ আলমালেকী (৬২৬-৬৮৪ হি.) ‘‘আযযখীরাহ’’ (২/৪৯০) ও ‘‘আলফুরূক’’ গ্রন্থে দালীলিক আলোচনার পর লেখেন-
وهذا حق ظاهر، وصواب متعين، أما وجوب الصوم على جميع الأقاليم برؤية الهلال بقطر منها فبعيد عن القواعد، والأدلة لم تقتض ذلك، فاعلمه.
অর্থ, ‘এ (অর্থাৎ প্রত্যেক দিগন্তে নিজেদের চাঁদ দেখা প্রযোজ্য হওয়া) স্পষ্ট বিধান; বরং এ-ই নির্ধারিত। কোনো ভূখন্ডে চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার দ্বারা সকল ভূখন্ডের অধিবাসীর উপর রোযা ফরয হওয়ার বক্তব্য (শরীয়তের) নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং শরীয়তের দলিলসমূহের দাবিও তা নয়। (আলফুরূক, কারাফী ২/৩০২ ফরক : ১০২)
তবে মনে রাখতে হবে, কারাফী উপরের কথাটি নিজের গবেষণা অনুসারে বলেছেন। একে মালেকী মাযহাবের সাথে সম্বন্ধ করেননি; বরং মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কওলের উপর আপত্তি আকারে পেশ করেছেন।
6. ইবনে জুযাই আলকালবী (৬৯৩-৭৪১ হি.)
ইমাম আবুল কাসেম মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ ইবনে জুযাই আলকালবী আলমালেকী ৭৪১ হিজরীতে যার শাহাদত, তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব ‘‘আলকাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যাহ’’য় লেখেন-
إذا رآه أهل بلد لزم الحكم غيرهم من أهل البلدان، وفاقا للشافعي، خلافا لابن الماجشون، ولا يلزم في البلاد البعيدة جدا، كالأندلس والحجاز إجماعا.
এখানে ইবনে জুযাই মালেকী রাহ. পরিষ্কার বলেছেন যে, অনেক দূরের শহর-নগরে যেমন আন্দালুস ও হিজায, এক শহরের চাঁদ দেখা অন্য শহরের জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় (লাযিম) না হওয়া ইজমায়ী বা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। (আলকাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যাহ, পৃষ্ঠা : ৮৯, আলকিসমুল আওয়াল, কিতাবুস সিয়াম)
7. ইবনে আরাফা (৭১৬-৮০৩ হি.)
অষ্টম হিজরী শতকে মালেকী মাযহাবের অনেক বড় ব্যক্তিত্ব
আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আরাফাও ইবনে আবদিল বার রাহ.-এর বক্তব্য নকল করে এর সমর্থন করেছেন।
ইবনে আরাফার ‘‘আলমুখতাসারুল কাবীর’’ আমার কাছে নেই। আর তাঁর ‘‘আলমাবসূত ফিল ফিকহ’’ সম্ভবত এখনো পান্ডুলিপি আকারে আছে। তবে তাঁর বক্তব্য ‘‘মাওয়াহিবুল জলীল’’ হাত্তাব (৩/২৮৪), ‘‘তাবয়ীনু উজূহিল ইখতিলাল ফী মুসতানাদি ইলানিল আদলিয়্যাতি বিছুবূতি রুয়াতিল হিলাল’’, আবদুর রহমান ইবনে যায়দান (পৃষ্ঠা : ৭৪), এবং ‘‘আলআযবুয যুলাল’’ (১/২৭)-এ নকল করা হয়েছে।
8. আবু আবদিল্লাহ আলহাত্তাব আলমালেকী (৯০২-৯৫৪ হি.)
আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আবু আবদিল্লাহ আলহাত্তাব ‘‘মুখতাসারু খলীলে’’র প্রসিদ্ধ ও সমাদৃত ভাষ্যকার। তিনি তার শরহে, ইবনে আরাফার সূত্রে আবু উমার ইবনে আবদুল বার রাহ.-এর কথা নকল করেছেন যে, অনেক দূরের এলাকায় এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য ধর্তব্য না হওয়া সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত। আর একে তিনি تنبيه শিরোনামে উল্লেখ করেছেন, যা বাংলায় অনেকটা ‘বিশেষ দ্রষ্টব্য’ শিরোনামের সমার্থক।
تنبيه : قال ابن عرفة : قال أبو عمر : وأجمعوا على عدم لحوق حكم رؤيته ما بعد كالأندلس من خراسان.
(মাওয়াহিবুল জলীল শরহু মুখতাসারি খলীল, হাত্তাব মালেকী ৩/২৮৪)
এ বিষয়ে মালেকী ফকীহগণের আরো বরাত-উদ্ধৃতির জন্য আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব-এর কিতাব ‘‘আলআযবুয যুলাল ফী মাবাহিছি রুয়াতিল হিলাল’’ অধ্যয়ন করা যায়, যা কাতারে শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম আনসারী রাহ.-এর তত্ত্বাবধানে মোটা মোটা দুই ভলিউমে প্রকাশিত হয়েছে।
এ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে আমার পক্ষে আরো বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই।
(আগামী সংখ্যায় পড়ুন : হাম্বলী মাযহাব ও অন্যান্য)